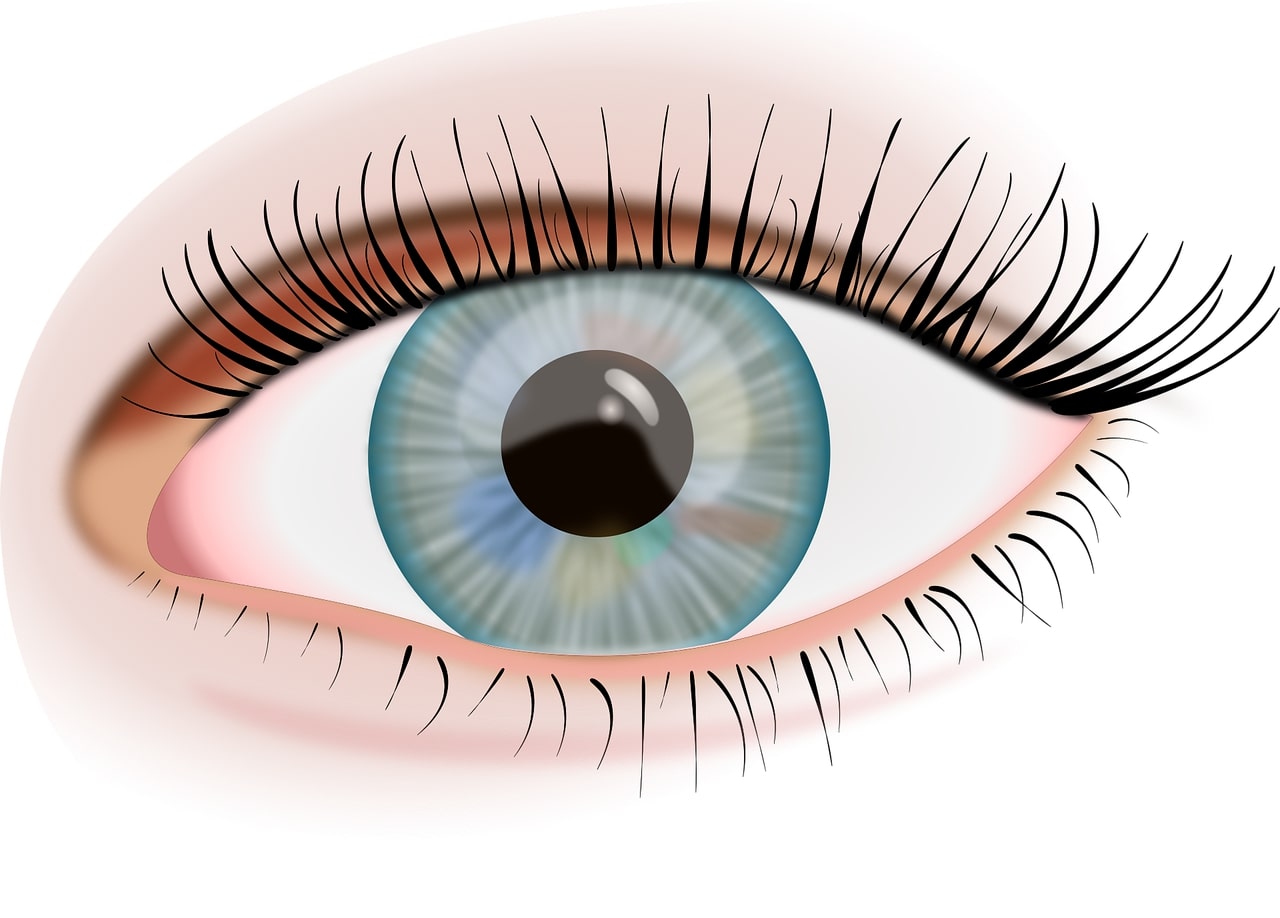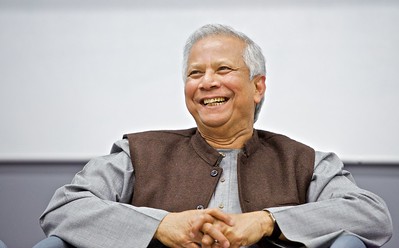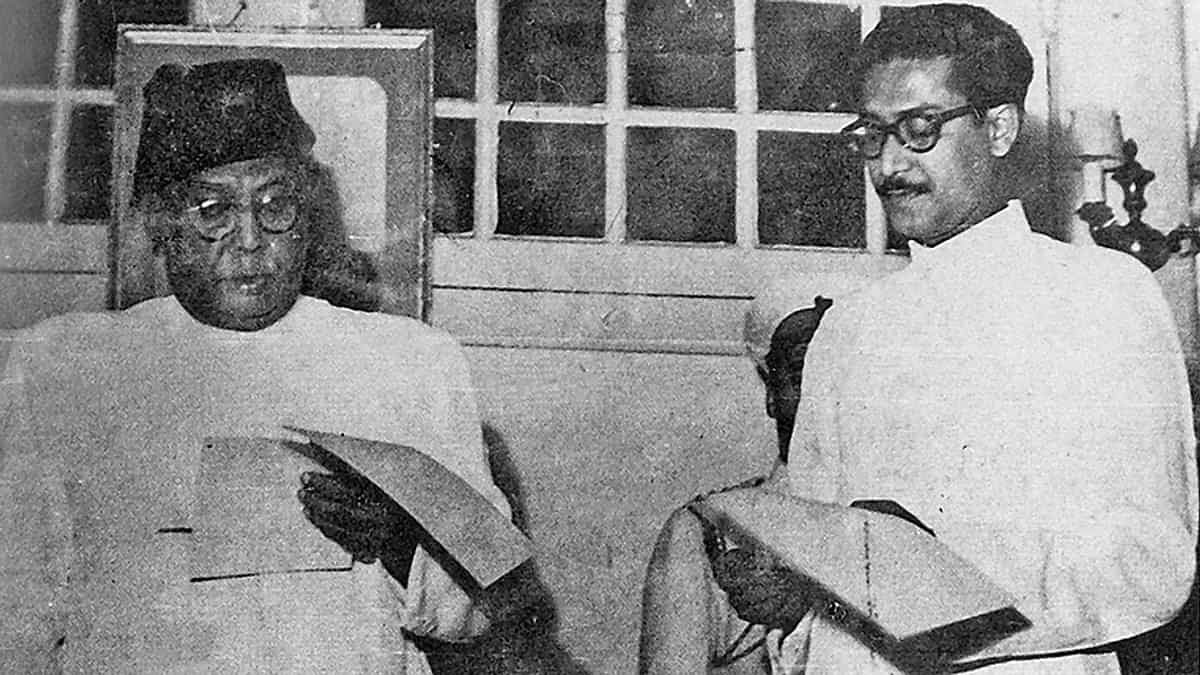অর্থপাচার কী এবং অর্থপাচার সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা
- প্রকাশ: ০৩:২১:১৫ অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ২৯ নভেম্বর ২০২২
- / ৭৫৮ বার পড়া হয়েছে
অর্থ বিষয়ে কিছু ভুল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অর্থপাচারকে ডলার-টাকার বান্ডিলের পাচারের সঙ্গে তুলনা করি, যা সব সময় ঠিক নয়। কিছুদিন আগেও দেশের প্রথম সারির একটা দৈনিকে দেখেছি অর্থপাচার বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং টাকার কিছু বান্ডিলের ছবি দেওয়া হয়েছে। অর্থপাচারকে এ রকম একটা দৃশ্যমান রূপ দিয়ে থাকার কারণে মনে করি যে টাকার বান্ডিল পাচার হয়ে যাচ্ছে। অর্থপাচার বলতে যা বোঝানো হয় তা আসলে কী?
অর্থ কী, তা না বুঝেই অর্থপাচারের ধারণা থেকে আলাপ শুরু করলে আমরা জটিল সমস্যা তৈরি করি। তার চেয়ে বরং বিষয়টির আলাপ সরলভাবে শুরু করাই ভালো। সেটি হলো, অর্থের বৈধ আদান-প্রদান কীভাবে হচ্ছে তা বোঝা। এটা কীভাবে ঘটছে সেটি বুঝতে পারলে অর্থপাচার ব্যাপারটাও বুঝতে পারব। অর্থের বৈধ আদান-প্রদান সবসময়ই হচ্ছে। আমরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকা পাঠাচ্ছি কিংবা কেউ চট্টগ্রামে বসে ঢাকায় টাকা পাঠাচ্ছে। আসলে কী ঘটছে? এ জায়গাটি বুঝলে অর্থের যে চলাচল ঘটে, সেটি আমরা বুঝতে পারব। তারপর অর্থপাচার, যেটি অনেক বেশি জটিল, সেটিও আমরা বুঝতে পারব। তাই বৈধ পন্থায় অর্থের আদান-প্রদান থেকে কথা শুরু করাই ভালো হবে।
প্রথমেই আমাদের অর্থের বস্তুগত ধারণা থেকে বের হতে হবে। আমরা অর্থকে খুব বস্তুগতভাবে দেখি। যেমন টাকার বান্ডিল বা কয়েন। ইদানীং হয়তো ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে ধরতে পারি। কিন্তু তাও আসলে বস্তুগত। অর্থের হয়তো বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে। কিন্তু অর্থ আসলে বস্তুগত কিছু নয়। তা আসলে একটা বিমূর্ত ধারণা। ভাষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে তাকে তুলনা করা যায়। সব জায়াগায় আছে, কিন্তু হাত দিয়ে বলা যায় না, এ জায়গাটা সংস্কৃতি। তেমনি অর্থও একটা বিমূর্ত বিষয়, কিন্তু মাঝে মাঝে সে মূর্ত রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন টাকার বান্ডিল বা কয়েন কিংবা স্বর্ণমুদ্রা কিংবা ইলেকট্রিক সিগন্যাল। এ জায়গাটা বোঝা আসলে সবার আগে দরকার।
অর্থ আসলে কী? সবচেয়ে সহজভাবে বলা যায় যে, মূলত অর্থ হলো ক্রয়ক্ষমতার সক্ষমতা। কারো ক্রয়ক্ষমতা আছে মানেই তার কাছে অর্থ আছে। বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন আমরা বৈধভাবে অর্থ এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাঠাচ্ছি। এক শহর থেকে আরেক শহরে পাঠাচ্ছি। কিংবা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে পাঠাচ্ছি। আমার কথাই ধরা যাক। আমি যুক্তরাজ্যে থাকি, এখানে আয় করি পাউন্ডে। ধরা যাক, আমি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের কাছে গেলাম। দেশের কাউকে আমি বললাম, আপনার কাছে ৫০০ পাউন্ড পাঠাচ্ছি। দেশে সে কি পাউন্ড পাচ্ছে? পাচ্ছে না, বরং পাচ্ছে টাকা। তার মানে আমার পাউন্ডটা কিন্তু তার কাছে গেল না। এ উদাহরণটাই দেখায় যে অর্থ আসলে নোটের বান্ডিল বা কয়েন নয়, সে রকম ধারণা থেকে তাই আসলে বের হওয়া দরকার। আসলে কী হচ্ছে? এমন হতে পারে ব্যাংক থেকে তুলে আমি ৫০০ পাউন্ড নিয়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে গেলাম। বললাম, নাও আমার ৫০০ পাউন্ড। এই সমমূল্যের টাকা তুমি বাংলাদেশে পাঠাও। অথবা এমনও হতে পারে, আমার ব্যাংক হিসাব থেকে ৫০০ পাউন্ড নিয়ে সেই সমমূল্যের টাকাটা বাংলাদেশে পাঠাতে বললাম। এর মানে হলো, আমি আমার ৫০০ পাউন্ডের ক্রয়ক্ষমতা পরিত্যাগ করলাম। বাংলাদেশে যে গ্রহীতা আছেন, তাকে টাকাটা বান্ডিল হিসেবে দেওয়া হলো অথবা তার ব্যাংক হিসাবে দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত যা হলো তা হলো, প্রাপকের জন্য টাকায় ৫০০ পাউন্ডের সমমূল্যের ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হলো। তাই আসলে এ বিনিময়টা হচ্ছে ক্রয়ক্ষমতার বিনিময়। এ উদাহরণে টাকা বৈধ পথে পাঠানো হচ্ছে। অর্থ বৈধ পথে কীভাবে যাচ্ছে, সেটি বুঝলে অবৈধ পথে যাওয়াটা বুঝতে পারব। অবৈধ পথটা হয়তো আমরা সঠিকভাবে জানি না। তবে বৈধ পথের মতো ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। এটা হয়তো আন্ডার ইনভয়েসের মাধ্যমে মাঝেমধ্যে হয়। বিদেশ থেকে যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা হলো, তার দামটা হয়তো কম দেখানো হলো। কিন্তু টাকা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্যুটকেসে চলে যাচ্ছে, সেটি ভাবলে আমরা খুব ভুল করব। কারণ ওই টাকাটা আমরা খুঁজে পাব না।
এটি সত্য, আমরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার সময় কিছু মুদ্রা বহন করি। কিন্তু সেটি খুব নগণ্য। সেটি বিবেচনা করার তেমন কিছু নেই। মূলকথা হলো, আমরা যদি ভাবি যে স্যুটকেস ভর্তি টাকা বহন করা হচ্ছে, তেমনটা হবে খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা। অনেকেই বলেন, ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তর করে স্যুটকেসে করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রকম হলেও তা খুবই নগণ্য পরিমাণে হচ্ছে। মূল বিষয় হলো, বৈধ বা অবৈধ হোক ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তরটা আসলে কীভাবে হচ্ছে। অর্থ পাচার বা অর্থ পাঠানোর সঙ্গে শারীরিক বা বস্তুগত মুভমেন্ট সবসময় মিলিয়ে না দেখাটাই হয়তো সঠিক।
ক্রয়ক্ষমতার পরিত্যাগ বা অন্য দেশে ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তরের বিষয়টিতে আসলে দেশের ভেতরে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা না করে মতামত দেওয়াটা মনে হয় সমীচীন নয়। আমরা শুনছি বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হচ্ছে। যেই অর্থে বলছি, সেটি হলো ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর। সেটি আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সেই বিশ্লেষণটা না করে ধারণা থেকে কিছু কথা বলতে পারি, যা নিয়ে আসলে পরিপূর্ণ গবেষণা করা দরকার। দেশের ভেতরে যে সবসময় খারাপ হচ্ছে তাও না। যেমন যখন ছাত্রছাত্রীরা বাইরে পড়তে যায় তখন দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাঠায়। সে ছাত্রটি শারীরিকভাবে চলে যেতে পারে বা শুধু তার ক্রয়ক্ষমতা দেশের বাইরে চলে যেতে পারে (অনলাইনে পড়াশোনা)। সেক্ষেত্রে দেশের সম্পদ, মাছ, পুকুর, গাছ কিন্তু আগের মতোই আছে। সেটি তো আর মুভ করল না। কাজেই যারা দেশে অবস্থান করছে বা দেশে যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে, সেই সম্পদ তারাই পাবে ভোগের জন্য। বিদেশে যে ক্রয়ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, তার তো দেশে ক্রয়ক্ষমতা নেই!
আরেকটা বিষয় বিবেচনার হলো, বাংলাদেশে পাউন্ডে কিছু কেনা যায় না। সব টাকার মাধ্যমেই কিনতে হবে। এখন দেশে কেউ তার টাকার ক্রয়ক্ষমতা পাউন্ডে নিয়ে গেলেন। সেই পাউন্ডটা বাংলাদেশে আছে না বিদেশে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাউন্ড দিয়ে কিছু কেনা যায় না। পাউন্ডটাকে টাকায় রূপান্তর করে তবেই কেনা যায়। কাজেই কেউ যদি টাকায় যে ক্রয়ক্ষমতা তা পাউন্ডে রূপান্তর করে নেয়, সে দেশে থাকল না বাইরে, সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। দেশে টাকায় তার যে ব্যয় করার ক্ষমতা, সেটি সে প্রত্যাহার করেছে। কাজেই দেশে যারা আছে তারা লাভবান হচ্ছে। এভাবে ব্যাপারটা দেখা যায়।
আবার যদি এমনভাবে হয় যে টাকায় তার যে ব্যয় করার ক্ষমতা, সেটি সে প্রত্যাহার করেনি, তাহলে কিন্তু যারা দেশে আছে তারা খুব একটা লাভবান হচ্ছে না। আরেকটি বিষয় হলো, ধরা যাক কেউ টাকার ক্রয়ক্ষমতা পরিত্যাগ করে পাউন্ডের ক্রয়ক্ষমতা গ্রহণ করল কিংবা ডলারের ক্রয়ক্ষমতা গ্রহণ করল। কিন্তু সেই লোকটি কোথায় আছে কে জানে? যে দেশে সে অবস্থান করছে সেখানে তো তার যে ক্রয়ক্ষমতা আছে, সেটি বিবেচনা করার ব্যাপার আছে। এখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টিও দেখার আছে যে অর্থপাচারের পাচারকৃত অর্থ কি অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ? তেমনটি হলে তা সামাজিক ন্যায়বিচারের জায়গাটি নড়বড়ে করে দেয়। এগুলো বিবেচনা করার বিষয় আছে।
আরেকটি বিষয় হলো, অর্থের চলনের সঙ্গে সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একটা যোগ আছে বলা হয়। যদি অর্থ বিদেশে যাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে হয়তো দেশের সামাজিক জীবনে নানা রকম অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি তো আছেই। তার ওপর দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি একটা দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা বিদেশে চলে যায়। বিদেশে অবস্থানকারী লোকজনের যদি দেশের সম্পদের ওপর অধিকার থাকে, তাহলে দেশের মানুষের ভাগে কম পড়বে। কাজেই বণ্টনের দিক থেকে দেখার একটা বিষয় আছে।
ধরুন, বৈধভাবে একজন ছাত্র হয়ে আরেক দেশে যাচ্ছে। এজন্য দেশ থেকে সে বাইরে টাকা পাঠাচ্ছে। ধরলাম, তাকে ৫ লাখ টাকা টিউশন ফি হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। তাকে সেই ৫ লাখ টাকা সমমূল্যের ডলার বা পাউন্ড দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। এটা তার কারো কাছ থেকে কিনতে হবে। তার তো ক্রয়ক্ষমতা ছিল টাকায়, সে ক্রয়ক্ষমতা পাউন্ডে পরিবর্তন করে তাকে টিউশন ফি পরিশোধ করতে হবে। এখন এ পাউন্ড সে কার কাছ থেকে পাবে?
আমরা জানি, সব বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে। বৈধ পথে হলো তা বাংলাদেশের ভেতরের কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাউন্ডটা সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই ছাত্রটি যখন টিউশন ফি পরিশোধ করছে, সে আসলে বাংলাদেশের ভেতরে পাউন্ডের যে ক্রয়ক্ষমতা বা ডলারের যে ক্রয়ক্ষমতা, সেটি গ্রহণ করে তা বাইরের একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করছে। সেই যুক্তিতে যখনই আমরা কিছু ক্রয় করছি অন্য মুদ্রায় তখনই নিজেদের বৈদেশিক ক্রয়ক্ষমতার কিছুটা পরিত্যাগ করছি। অর্থপাচারটা সেই অর্থে দেশের বৈদেশিক মুদ্রায় যে ক্রয়ক্ষমতা, সেটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা কমায়। যে-কোনো ধরনের আমদানিও সেটিই করবে। অর্থপাচারের সঙ্গে সেদিক থেকে আমদানির আসলে তেমন কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। আমদানিও যেমন ক্রয়ক্ষমতা কমায়, তেমনি অর্থপাচারও ক্রয়ক্ষমতা কমায়। বৈধ পথে হলে সেটি অর্থনীতিতে সার্কুলেট করে। ফলে এতে বিভিন্ন রকম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কিছুটা সাহায্য করে। অবৈধ পথে হয়তো সেভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে না।
এখানে আলোচনাটা অনুমাননির্ভর। আসলে কী হচ্ছে আমরা জানি না, কারণ অর্থপাচার দৃশ্যমান নয়। যেমন হুন্ডি। হুন্ডির কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু দেখি না। হুন্ডি হলো বাইরে একজন কর্মরত লোক নিজের আয়টা সে দেশের একজন প্রতিনিধিকে দিয়ে দেয়, সেই মুদ্রাটা সেখানেই থেকে যায় আর বাংলাদেশে একজন তাকে সমমূল্যের টাকা দিয়ে দেয়। এটিই হলো হুন্ডি। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নও অনেকটা সে রকমই প্রায়। কিন্তু একটু ফরমাল সিস্টেম; তারা বৈধ। কর দেয়, ফি নেয় ইত্যাদি। হুন্ডিতে সমস্যা হলো, এর আনুষ্ঠানিক কোনো হিসাব থাকছে না। মানুষ বিদেশে বসে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাচ্ছে। তাতে বাংলাদেশে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে। সেটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সার্কুলেট হয়, যদি সে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে তা পাঠায়। তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা অধিকার সৃষ্টি হয় ওই বৈদেশিক মুদ্রার ওপর। এভাবে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভটা বাড়ে। হুন্ডিতে মূল সমস্যা হলো, এর মাধ্যমে আসা অর্থে বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশে কোনো ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে না। আগে যা ছিল তা-ই থাকে।
সেক্ষেত্রে অর্থপাচারের ক্ষেত্রে হয়তো একই রকম কিছুটা হবে। যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ টাকা দিয়ে দেয়, তার বিনিময়ে যদি পাউন্ড, ইউরো বা ডলার পায়, সেটি যদি বাংলাদেশি কোনো ব্যাংকের মধ্য দিয়ে না যায়, তাহলে রিজার্ভ আগে যা ছিল তা-ই থাকবে।
এখানে ভয়ের একটা বিষয় ঘটতে পারে। ধরা যাক, বাংলাদেশ থেকে কেউ টাকা প্রদান করল বাইরের কোনো ব্যক্তিকে। তার বিনিময়ে পাউন্ড বা ডলারে ক্রয়ক্ষমতা গ্রহণ করল। যে বিদেশী গোষ্ঠী বা ব্যক্তি টাকাটা (টাকায় ক্রয়ক্ষমতা) পেল, সে বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। এ জায়গাটাও বিবেচনার বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশে যে-কোনো কিছু করতে গেলে টাকা লাগবে, যেহেতু এখানে অন্যান্য মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা নেই। কাজেই টাকা পাওয়া মানে বাংলাদেশের ভেতরে তার কিছু করার সক্ষমতা বাড়ল। সেটি হয়তোবা বাংলাদেশের জন্য সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে মঙ্গলজনক নয়।
আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ— তা হলো একটা দেশে কিছু অর্থ থাকা প্রয়োজন, যা নানা কর্মকাণ্ডকে গতি দেয়। সেটি যদি সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে এর প্রভাব পড়বে। ধরা যাক, সামান্য হলেও কিছু টাকা ক্যাশ করে বাইরে নিয়ে আসা হলো। এতে দেশের ভেতরে অর্থের যে সার্কুলেশন ছিল তা কিছুটা কমে গেল। পর্যাপ্ত অর্থের সার্কুলেশন না হলে দেশের ভেতরে ক্রয়-বিক্রয়ের কর্মকাণ্ড আছে, তাতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এখন সবকিছুতে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সেই অর্থটা প্রত্যাহার করার মানে হলো বিনিময় কমে গিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। সেই অর্থ প্রত্যাহারের পরিমাণ দেশের অর্থের সার্কুলেশনের তুলনায় কত তাও বিবেচনার বিষয় রয়েছে।

অর্থের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থ সরকারি-বেসরকারি উভয়ভাবেই সৃষ্টি হয়। যখনই আমি আমার ক্রয়ক্ষমতা পরিত্যাগ করে আরেকজনকে দিলাম, আসলে ওই মুহূর্তে আমি অন্যের জন্য অর্থ সৃষ্টি করছি। সরকার যে টাকা ইস্যু করে সেটিই শুধু অর্থ নয়। এর বাইরে বিপুল পরিমাণ প্রাইভেট মানি অবস্থান করে। বৈধভাবেই অবস্থান করে, অবৈধ কিছু নয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ সবসময়ই ক্রয়ক্ষমতা বিনিময় করছে। তার মাধ্যমে অর্থ তৈরি হচ্ছে। সেটি সবসময় হবে। কিন্তু সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটি যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়, তেমনটি হলে বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। দাম বেড়ে যায়, কমে যায়। এ কারণে অবৈধভাবে অর্থপাচার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।
প্রথম প্রকাশ: বণিক বার্তা