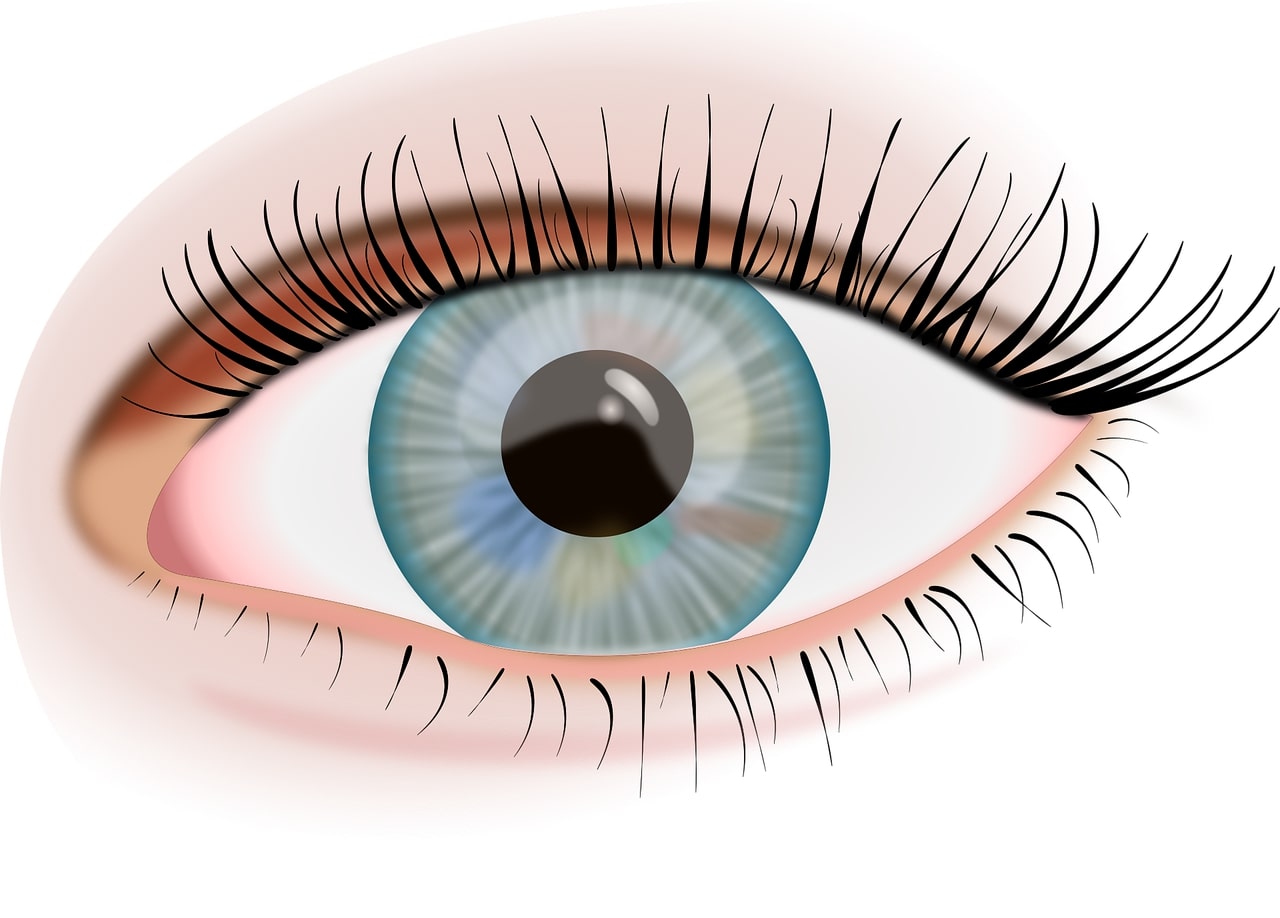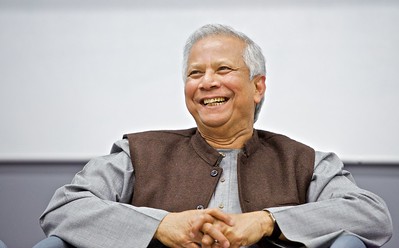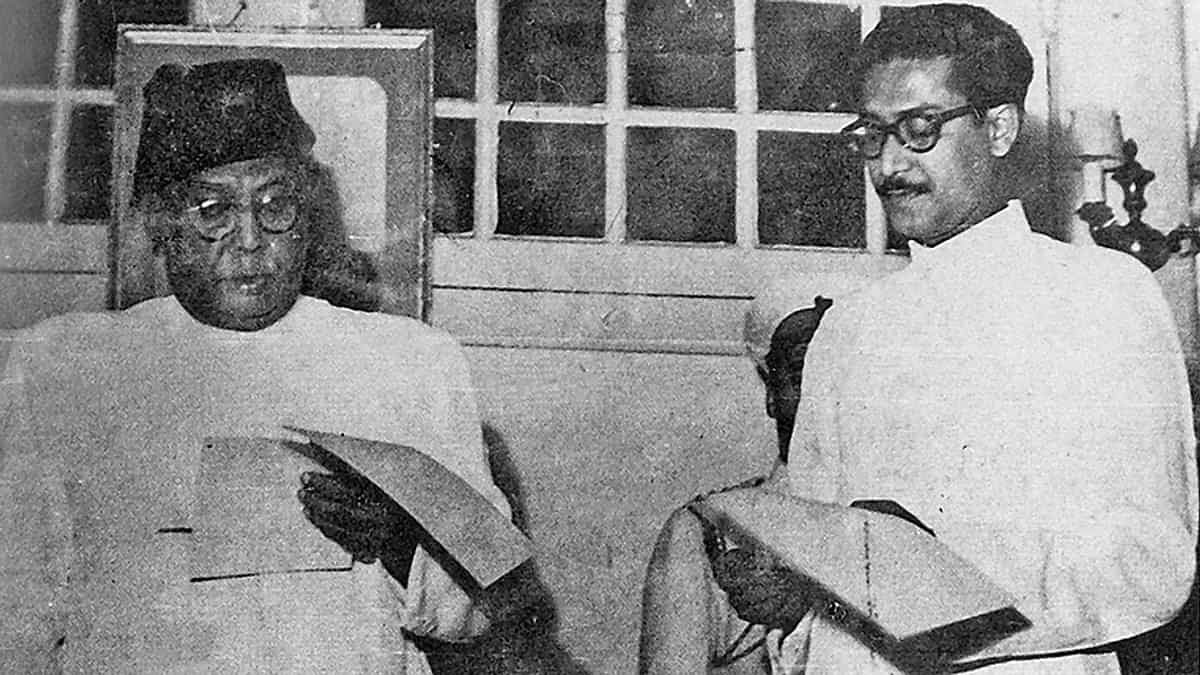ওষুধের অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি কেন?
- প্রকাশ: ০৬:৫৪:৪১ অপরাহ্ন, শুক্রবার, ১৪ অক্টোবর ২০২২
- / ৫৮৫ বার পড়া হয়েছে
ওষুধের যুক্তিহীন ব্যবহার ও প্রয়োগ বর্তমান বিশ্বের এক অন্যতম সমস্যা। ওষুধ ব্যবহারের সমস্যা জানতে হলে; ওষুধের নিরাপদ, যুক্তিসংগত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে সমস্যার উৎস, সমস্যা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা এবং তাদের মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।
সমস্যা চিহ্নিত না হলে ওষুধের যুক্তিসংগত প্রয়োগ এবং এর প্রকৃত উন্নয়ন কোনোমতেই সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, দেশের ক্লিনিক, হেলথ কমপ্লেক্স বা হাসপাতালগুলো ওষুধের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের মূল উৎসগুলোর অন্যতম। অনিয়ন্ত্রিত ওষুধের ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে ওষুধের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের দিক থেকে ড্রাগ স্টোরগুলোর অবস্থান বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে।
ডিগ্রিধারী ফার্মাসিস্টের অভাবে এবং ওষুধ ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে, অজ্ঞ-অশিক্ষিত লোকজন দ্বারা ড্রাগ স্টোর পরিচালিত হয় সাধারণত অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দোকানের মতো। কিন্তু ওষুধের দোকান আর মুদি দোকান বা কাপড়ের দোকান এক হতে পারে না।
ওষুধের অযৌক্তিক প্রয়োগের বড়ো উৎস হলো চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ও প্রেসক্রিপশন। চিকিৎসক ঠিকমতো রোগ নির্ণয় করে যুক্তিসংগতভাবে ওষুধ প্রদান না করলে রোগী ওষুধের অপব্যবহারজনিত সমস্যার শিকার হবে। চিকিৎসক তার দায়িত্ব সঠিক ও নির্ভুলভাবে পালন করলেও ওষুধের ডিসপেন্সিং যুক্তিসংগত বা সঠিক না হলে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
অন্যদিকে, প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধ সম্পর্কে রোগীকে পর্যাপ্ত ও প্রকৃত তথ্য, পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করা না হলে যুক্তিহীন ব্যবহারের কারণে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রোগীর জন্য প্রেসক্রিপশনে ওষুধ প্রদানে চিকিৎসক যত সতর্কতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবেন, রোগী তত বেশি উপকৃত হবে। রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধে চিকিৎসকদের ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।
আমাদের দেশে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে-চিকিৎসক এলে ওষুধ ছাড়াই রোগীর অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে যায়। এর পেছনে বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে। কারণ রোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় শরীর ও মনের যোগসূত্র অভিন্ন। উন্নত বিশ্বে প্রকৃত চিকিৎসা শুরুর আগেই চিকিৎসকরা প্রায়ই রোগীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাঙা করার উদ্যোগ নেন। রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রদান এবং চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করতে চিকিৎসকরা সদা সচেষ্ট থাকেন। এতে রোগীর আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। রোগীও সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তথ্য জানার জন্য চিকিৎসককে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন।
ফলস্বরূপ রোগ নির্ণয় ও ওষুধ প্রয়োগে ভুল কম হয় বলে ওষুধের অপব্যবহারও কমে আসে। তারপরও দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকরা তাদের প্রেসক্রিপশনে যেসব ওষুধ লিখে থাকেন, তার সবই যুক্তিসংগতভাবে লেখেন না। ওষুধের এ অযৌক্তিক প্রয়োগের পেছনে বহুবিধ কারণ কাজ করে। বহু চিকিৎসক পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে রোগীকে সঠিক ওষুধ প্রদানে সক্ষম হন না।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব চিকিৎসক নিজেদের যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন না। এসব চিকিৎসক সাধারণত সনাতনী পদ্ধতিতে যুগ যুগ ধরে সেকেলে মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যান বলে রোগ নির্ণয় বা ওষুধ প্রদানে প্রায়ই ভুল হয়।

আমাদের মতো দেশে অতিমাত্রায় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে রোগীর প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে চিকিৎসকরা অসতর্কতা ও অবহেলার কারণে রোগীকে সঠিক চিকিৎসা প্রদানে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে পৃথিবীজুড়েই বহু চিকিৎসক ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক প্রভাবান্বিত ও প্রলুব্ধ হয়ে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও দামি ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন।
ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধ বাজারজাত করার পর ওষুধ প্রমোশনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে তাদের ওষুধের কাটতি বাড়ানোর জন্য। উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ওষুধের প্রমোশনে এবং পলিটিক্যাল লবিংয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ ব্যয়ভার বহন করতে হয় নিরীহ ক্রেতা বা রোগীকেই।
ওষুধের কাটতি বাড়ানোর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোর মূল টার্গেট চিকিৎসক। কারণ চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধ লেখেন, রোগী মূলত সেই ওষুধই কিনে থাকে। অধিক হারে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ওষুধ কোম্পানিগুলো সাধারণত টনিক, ভিটামিন, হজমিজারক, বলবৃদ্ধিকারক, এনজাইম, কফ মিকচার, এলকালাইজার ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদনে বেশি তৎপর থাকে।
কারণ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের চেয়ে এসব তথাকথিত ওষুধের ওপর মুনাফার হার বহুগুণ বেশি। এ মুনাফার হার আরও অনেকগুণ বেড়ে যায়, যখন চিকিৎসকরা তাদের প্রেসক্রিপশনে এসব ওষুধ নামধারী পণ্য নির্বিচারে প্রেসক্রাইব করেন। ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে এসব ওষুধ প্রেসক্রাইবারদের সম্পর্ক যতটা না পেশাগত, তার চেয়ে বেশি ব্যবসায়িক।
এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অগ্রগামী হলেও ছোটো-বড়ো, প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ওষুধ কোম্পানি চিকিৎসকদের পেছনে কম-বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকে। ব্রিটেনে চিকিৎসকপিছু ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রতিবছর তিন লাখ টাকা ব্যয় করে। বাংলাদেশে এ ব্যয়ের পরিমাণ কত তা কে জানে। এ তো গেল অর্থের কথা। অর্থ ছাড়াও ওষুধ কোম্পানিগুলো চিকিৎসকদের প্রচুর পরিমাণ ওষুধ ফ্রি স্যাম্পল হিসাবে উপহার দিয়ে থাকে।
অভিজ্ঞ মহল মনে করে, এ ফ্রি স্যাম্পল আর ঘুসের মধ্যে পার্থক্য অতি নগণ্য। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, চিকিৎসকরা এই ফ্রি স্যাম্পল কেন গ্রহণ করেন বা এ ওষুধ নিয়েই বা তারা কী করেন? এভাবে ফ্রি স্যাম্পল নেওয়া বা দেওয়া নীতিগতভাবে বৈধ হতে পারে না।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশেও প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধের পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে যেসব ওষুধ লিখে থাকেন, তার মধ্যে অকেজো বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের পরিমাণ প্রায় ৩৩ শতাংশ। ফ্রান্সে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ডেন্টাল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ৪৫ শতাংশই অপ্রয়োজনীয় বলে অভিজ্ঞ মহল মত পোষণ করে।

বয়স্ক লোকদের বেলায় ওষুধ প্রয়োগের ৫০ শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো মেডিকেল রুল অনুসরণ করা হয় না বলে অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। এসব অপ্রয়োজনীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করার জন্য চিকিৎসকদের অমনোযোগ ও অজ্ঞতাকে দায়ী করা হয়। ব্রিটেনে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, যেসব মহিলা সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন, তাদের অনেককে প্রসবের আগের রাতে ঘুমের ওষুধ প্রদান করা হয়।
গর্ভবতী মায়েদের এভাবে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও এর সত্যিকার জবাব পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে, সত্যিকার অর্থে এ ওষুধ কার জন্য? মা, নাকি বাচ্চার জন্য? নাকি চিকিৎসক এবং মেডিকেল স্টাফদের জন্য, যারা রাতে শান্তিতে ঘুমাতে চান?
উন্নয়নশীল অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, সিডেটিভ, অ্যান্টিডায়ারিয়াল, ভিটামিন, টনিক, কফ মিকচার, স্টেরয়েড, অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টাসিডজাতীয় ওষুধ। টনিক ভিটামিনের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম দুর্বলতা রয়েছে। এ দুর্বলতার কারণ ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনৈতিক ড্রাগ প্রমোশন এবং চিকিৎসক কর্তৃক এসব ওষুধের ঢালাও প্রয়োগ। টনিক ও ভিটামিন সম্পর্কে ওষুধ কোম্পানিগুলো যেসব ভ্রান্ত ধারণা চিকিৎসক ও জনসমক্ষে তুলে ধরে তার মধ্যে রয়েছে-টনিক ও ভিটামিন সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার, বয়স্কদের যৌবনপ্রাপ্তি, শিশুদের মেধা ও বয়োবৃদ্ধি, ত্বকের শ্রীবৃদ্ধি, চুল পড়া বন্ধ হওয়া ইত্যাদি। এসব বক্তব্যের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও বহু চিকিৎসক প্রায়ই এসব বস্তু প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন। রোগী প্রয়োজনীয় মনে করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে এসব ওষুধ কিনে থাকে। এ অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার স্পষ্টতই প্রবঞ্চনার শামিল।
ওষুধের অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার ফলে রোগী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধের কোনটি প্রয়োজনীয়, কোনটি অপ্রয়োজনীয় বা প্রদত্ত ওষুধের সঙ্গে সৃষ্ট রোগের আদৌ সম্পর্ক রয়েছে কিনা এসব প্রশ্ন উপস্থাপন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রোগীরা সচরাচর রাখে না। ফলে রোগী প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ কিনতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রেসক্রিপশন মোতাবেক অপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিনলে রোগী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপ্রাসঙ্গিক বা ক্ষতিকর ওষুধ সেবন করে রোগী মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়া বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়। এ ক্ষতির দায়-দায়িত্ব থেকে চিকিৎসক অব্যাহতি পেতে পারেন না। উন্নত বিশ্বে রোগী চিকিৎসকের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। অনুন্নত দেশে রোগী এ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে না। কারণ, আমাদের মতো দেশে মনে করা হয় রোগী কমনম্যান, চিকিৎসক সুপারম্যান। তাই সুপারম্যানদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। মনে করা হয় ফিজিশিয়ানস আর অলওয়েজ রাইট, অর্থাৎ চিকিৎসকরা সবসময় সঠিক।
বাংলাদেশে ড্রাগ প্রমোশনে কোম্পানিগুলো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ড্রাগ প্রমোশন অফিসার নিয়োগ করে থাকে। দেশে প্রতি তিনজন চিকিৎসকের পেছনে একজন রিপ্রেজেনন্টেটিভ রয়েছে এবং এ খাতে প্রতিবছর কম করে হলেও দুই হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। এ রিপ্রেজেনন্টেটিভরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওষুধ বিশেষজ্ঞ নয় এবং কোনো কোনো সময় ওষুধের ওপর এদের পর্যাপ্ত জ্ঞানও থাকে না। তাদের কোনো কোনো সময় ড্রাগ প্রমোশনের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ড্রাগ প্রমোশনের জন্য ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ কতটুকু নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত তথ্যসাপেক্ষ তা মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এরা সাধারণত কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থটাকে বড়ো করে দেখে এবং সে মোতাবেক চিকিৎসককে ওষুধ প্রয়োগ এবং ড্রাগ স্টোরগুলোকে ওষুধ কিনতে প্রলুব্ধ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো রোগের ক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচনে প্রকৃত তথ্য না পেলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত হয়। এতে ভুল বা ক্ষতিকর ওষুধ প্রয়োগের ফলে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ওষুধ কোম্পানিগুলো কর্তৃক চিকিৎসক ও রোগীর জন্য প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা বিধান করার ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু তা নেওয়া হয় কি?
বর্তমানে ওষুধের জোয়ারে আমাদের চিকিৎসকরা ভাসছেন আর এত সব ওষুধের ওপর প্রকৃত তথ্য অন্বেষণে হিমশিম খাচ্ছেন। কোনো দেশে ওষুধের সংখ্যায় সীমাবদ্ধতা না থাকলে এবং বাজার প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় ওষুধে ভরে গেলে সব ওষুধের ওপর সম্যক ধারণা অর্জন কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুচিকিৎসার জন্য সীমাবদ্ধ ওষুধের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞান অসংখ্য ওষুধের ওপর অপূর্ণ ও ভাসাভাসা জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি উপকারী। ওষুধের ফলপ্রসূ ও যুক্তিসংগত প্রয়োগের জন্য কোম্পানি প্রদত্ত নামের পরিবর্তে ওষুধের জেনেরিক নাম ব্যবহার আবশ্যক।
প্রত্যেক দেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা থাকা প্রয়োজন। সুচিকিৎসার স্বার্থে চিকিৎসকদের জন্য থাকা প্রয়োজন একটি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের নিরীহ জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে এসব ইন্সট্রুমেন্টের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও তা-ই মনে করে।