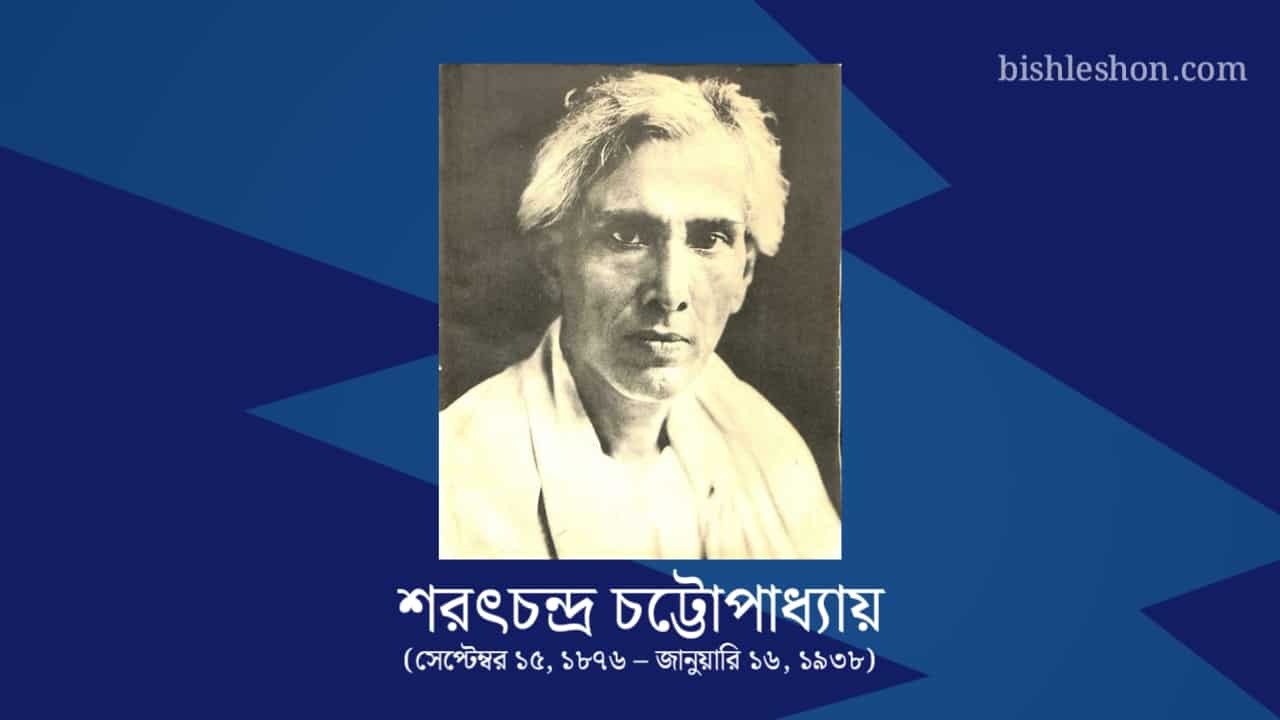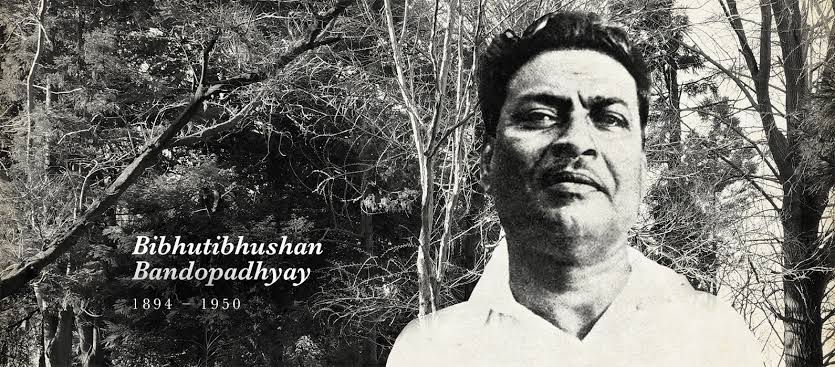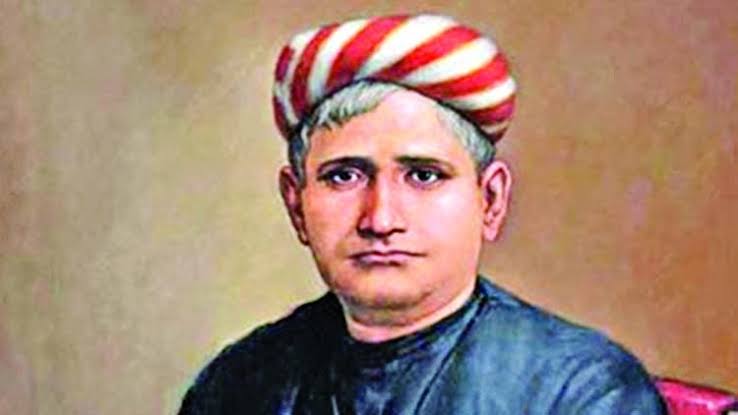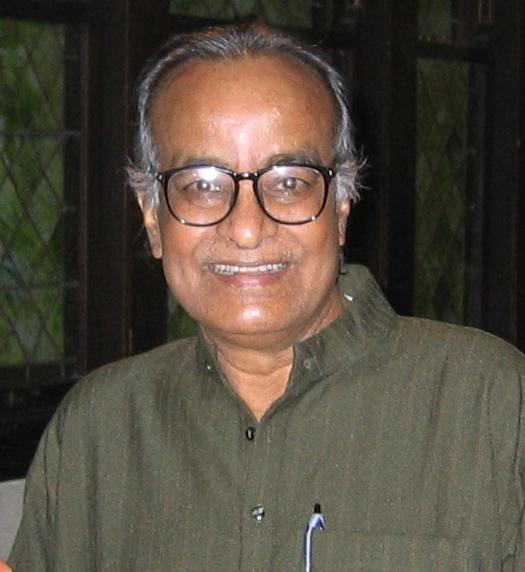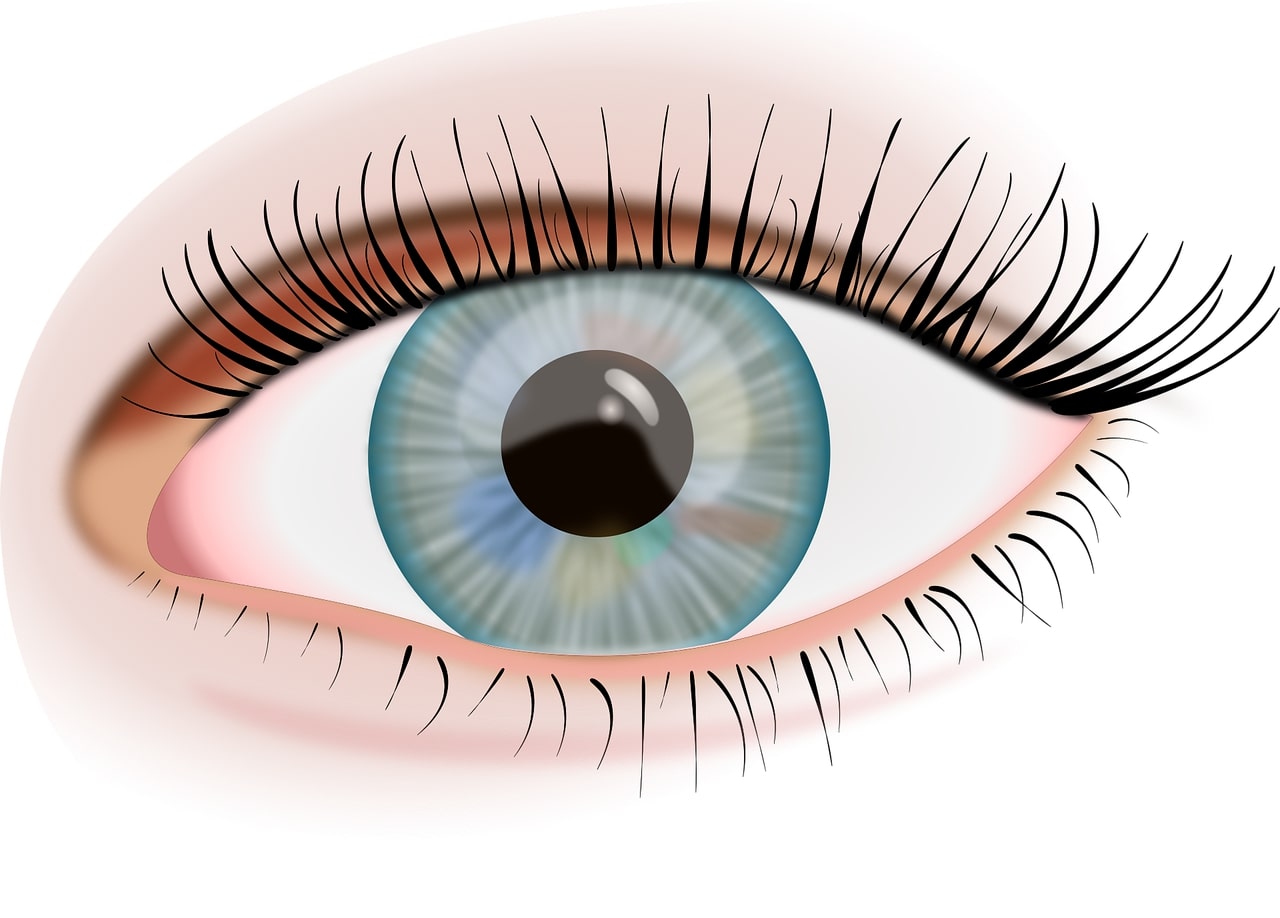রিভিউ: তিতাস একটি নদীর নাম
- প্রকাশ: ১০:০০:০০ পূর্বাহ্ন, শনিবার, ১৪ অগাস্ট ২০২১
- / ১৪০৩০ বার পড়া হয়েছে

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি নিম্নজীবী মানুষের এক অনুভবী বাস্তবতার নাম, যেখানে ফুটে উঠেছে বাস্তুচ্যুত শিল্পীর যন্ত্রণা
অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা উপন্যাসের একজন অকৃত্রিম শিল্পী। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর শিল্পের সারাৎসার। গোকর্ণঘাটের তিতাস তীরবর্তী অঞ্চল যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেই মালোপাড়াই তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। তাই উপন্যাসটিতে ঘিরে রয়েছে শিল্পীর নিজস্ব জগতের এক গভীর অভিব্যক্তি। শুধু ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য নয় মালোজীবনের গভীর ও গোপনতম ব্যথা ও বেদনার সুর এ- উপন্যাসকে বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে। পটভূমির সত্যতা ব্যতিরেকেও মালোসমাজের অভ্যন্তরীণ মানুষের আবিষ্কার, পরিবেশগত ঘনিষ্ঠতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের নানামাত্রিক রূপায়ণ এ-উপন্যাসে ঘটেছে। মানুষের জীবন ও জীবিকার সীমাহীন সংগ্রাম, দুষ্ট-খল সমাজজীবনের ঘূর্ণিপাকে মানবিকতার বিরাট পরাজয়ও সেখানে বৃহত্তর ব্যাপ্তি লাভ করেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেখিয়েছেন- মানুষের জীবনের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও অমোঘ প্রকৃতি ও প্রবহমান কালের সত্য তার ট্র্যাজিক জীবনের মূল। এই ট্র্যাজেডি আবার ব্যক্তিমানুষের একার নয়; সমগ্র সমাজব্যাপী এক নিরুচ্চার সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে সে ক্রমশঃ ব্যক্তিমানুষেরই বেদনায় অভিষিক্ত। অবশ্য ব্যক্তিজীবনের বোধ এ-উপন্যাসে থাকলেও তা ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠে না। মধ্যবিত্তিক জীবন কাঠামোর বাইরে তা এক নিরেট বাস্তবতার প্রতিচ্ছায়া। নিম্নজীবী মানুষের কণ্ঠস্বরকে বাহ্যিক অর্থে নয় বরং অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্প রচনার এক অনুভবী বাস্তবতার নাম ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস।
এক নজরে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ পর্যালোচনা
- অল্প কথায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরিচিতি
- পর্যালোচনায় ‘তিতাস একটি নদীর নাম’
- তিতাসের বুকে ইতিহাস নাই, সে শুধু একটা নদী
- হাসির নামে কত বিষাদ
- তিতাস একটি নদীর নাম এবং মানবিক উত্থান-পতনের এক সার্বজনীন ইতিবৃত্ত
- তিতাস নদীর পাড়ের মালোসম্প্রদায়
- জেলেরাই পায় না বড়ো মাছের স্বাদ
- ধান থাকলেও চাষীদের জোটেনা গামছা
- ‘রাতের ঝড়ে পাখির যে ডানা ভাঙ্গিল, সে ডানা আর জোড়া লাগিল না।’
- অনন্তর মা বাসন্তীর ঘরভুক্ত
- মালোজীবনের শত দারিদ্র্য আর যন্ত্রণা
- ঘরের মালিক হলেও জমির মালিক নয়
- ধুতির দামে বিক্রি হয় মালো সমাজের মানুষ
- আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিবাদী মালোসমাজ
- আত্মবিক্রয় এবং মালোসমাজ ধ্বংসের একজন অনুঘটক
- কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না।
- মাছের মতো জন্ম, আবার মাছের মতোই মৃত্যু
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
- বিশ্বাস সংস্কার
- সরলমনা সুবল, মালিকশ্রেণি এবং বাসন্তী
- বাসন্তী আর অনন্তর মা
- কিশোর ও অনন্তর মায়ের মৃত্যু
- অনাথ অনন্ত
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো বেদনাময় জীবনের শিকার
- বাসন্তীর অনুধাবন: মা একমাত্র সত্য
- প্রতিবাদী নারী বাসন্তী
- ষড়যন্ত্র ও সর্বনাস
- মালোদের সাংস্কৃতিক শুদ্ধতার রক্ষা
- তিতাসের পাড়ের মালো সংস্কৃতির পরাজয় ও মোহনের কান্না
- তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি এবং আরও কিছু কথা
- সর্বশান্ত তিতাস নদীর পাড়ের মানুষ
- ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের নায়ক এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ
- শেষ কথা
অল্প কথায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরিচিতি
অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১ জানুয়ারি, ১৮৯১ সালে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপকণ্ঠে তিতাস তীরের মালোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ, মায়ের নাম অনাবিষ্কৃত।
তিন ভাই এক বোনের পরিবার তাদের। অল্প বয়সেই তাঁর সব ভ্রাতা মৃত্যুবরণ করে। একমাত্র বোন বিধবা হন অল্প বয়সে। অদ্বৈতর বাবা-মাও মারা যান তাঁর অপরিণত বয়সেই। এরপর সারাজীবন ধরে শুধু দুঃখ আর সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়ার বাধন।
অন্যের অর্থানুকূল্যে হাইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলোেও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি কলকাতা পৌঁছালেন জীবিকারোহনের আশায়।
‘ত্রিপুরা’, ‘নবশক্তি’, ‘মোহাম্মদী’, ‘আজাদ’ প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকায় কাজ করে শেষ পর্যন্ত সাগরময় ঘোষের সহায়তায় ১৯৪৫ সালে তিনি ‘দেশ’ পত্রিকায় যোগ দেন।
অদ্বৈত মল্লবর্মণের কলকাতার জীবন নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ছিল না। ফেলে আসা শিকড়ের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব টান। কলকাতার মেসবাড়িতে থাকার সময় আত্মীয়কৃত্য আর বই কেনার কাজে তার জীবনের সমুদয় অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন।
১৯৫০ সালের দিকে অদ্বৈত ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। প্রথমবার চিকিৎসা নিলেও সাগরময় ঘোষের চেষ্টায় দ্বিতীয়বারের মত কাঁচড়াপাড়া যক্ষা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হলোেও সেখান থেকে তিনি পালিয়ে আসেন। অবশেষে ১৯৫১ সালের ১৬ই এপ্রিল কলকাতার ষষ্ঠীতলার বাসায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
তিতাস নদীর মতই এ-শিল্পী অভিমানী। তিতাসের গোপন গভীর ষড়যন্ত্রের কথা হয়ত তিনি কান পেতে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই জীবনের ছন্দে প্রবহমান অথচ কালগর্ভে বিলীনপ্রায় তিতাসের পরাজয় মাল্য বরণের মত এক অপচয়ের বোধ তাঁর ব্যক্তিজীবনেও যেন তিনি বহনের দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন।
পর্যালোচনায় ‘তিতাস একটি নদীর নাম’
তিতাসের বুকে ইতিহাস নাই, সে শুধু একটা নদী
তিতাস নদীর বর্ণনা লেখকের তুলিতে শান্ত মধুরতা দিয়ে শুরু হয় কিন্তু কালের পরিণামী গ্রাস এখানকার মানুষকে করে পর্যুদস্ত। গোকর্ণঘাট গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শান্ত স্নিগ্ধ ও অথৈ জলে দুকূল উপচে পড়া এক নদী তিতাস। তিতাস ছোটো নদী; অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্যই আজ তা পরিচিত। কোনো ইতিহাস কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লবের খাতায় তিতাসের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। রচয়িতার ভাষায়, “তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী’। এ-নদীর পাড়ে বসবাসরত অবহেলিত অবজ্ঞাত শিক্ষা ও আধুনিক জীবনের সুবিধা-বঞ্চিত গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন। তিতাসকে কেন্দ্র করেই তাদের কষ্ট-বেদনা-হাসি-কান্না-ভালোবাসা উত্থিত হয় আবার মিলিয়ে যায়। এটাই এ-নদীর বিশেষত্ব। পদ্মা মেঘনার বিশালতা প্রচণ্ডতা এ-নদীর নেই। লেখকের বর্ণনায় :
“তিতাস কত শান্ত। তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়ের বুকেই মাথা এলাইয়া দিয়া শান্ত মনে জাল গুটাইতেছে।”
তিতাস নদী বৃহত্তর কোনো ইতিহাসের অংশীভূত না হলোেও নিজস্ব বিকাশের পথ তার রুদ্ধ নয়। পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসের অংশ না হলোেও জীবনধর্মের সত্য উচ্চারণে, নিম্নজীবী মানুষের আবেগের ভাষা ধারণে এবং অবহেলিত জেলে সমাজের কথকতায় তা পরিপূর্ণ। ফলে তিতাস তথাকথিত মূলধারার ঐতিহাসিক উপকরণ-সমৃদ্ধ না হলোেও লেখকের বর্ণনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামীণ মানুষের বাস্তবতার তা চরম সাক্ষী। তাই :
“পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌ-ঝিয়ের দরদের ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সে ইতিহাস কেউ জানে, কেউ হয়ত জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য। এর পাড়ে খাঁটি রক্তমাংসের মানুষের মানবিকতা আর অমানুষিকতার অনেক চিত্র আঁকা হইয়াছে।”
হাসির নামে কত বিষাদ
এ-উপন্যাসের ৪টি পর্ব ও ৮টি উপপর্বের প্রথম অংশের নাম ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। উপন্যাসের নামেই এ- অধ্যায়ের শিরোনাম লিখিত। এ-অংশে অবজ্ঞাত নদী তিতাসের বর্ণনার মোহনীয় ভাষাভঙ্গি গভীর দার্শনিক এক উপলব্ধি সঞ্চার করে পাঠক মনে। সে-সঙ্গে তিতাসকে কেন্দ্র করে মানুষের বাঁচা-মরার প্রসঙ্গ এবং জীবন-জীবিকার সীমাহীন জটিলতার আখ্যান হয়ে ওঠে তা। ’ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী’র মত বিশালতর সংগ্রামের কথা এখানেও আছে তবে তা ব্যক্তি মানুষের সংগ্রাম নয়। নদীর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতই এক কালিক প্রবহমানতা এখানে বিশালায়তনিক গোষ্ঠীজীবনের সামূহিক বাস্তবতার অংশ বলে পরিগণিত। মানুষের জন্ম এখানে অবহেলায়, বেড়ে ওঠা কষ্ট ও যাতনায়। জন্মে কোনো পাপ না থাকলেও জেলেপাড়ার শিশুরা বৈষম্যমূলক পৃথিবীর দেনার জালে ঋণগ্রস্ত। আগাছার মত মানব জন্ম এখানে। তাই আগাছার মতই প্রকৃতি সেগুলোকে ছাটাই-বাছাই করে। মানুষের শত মরণ ও কান্নার রোল তিতাসের চাপা বাতাস আর জলের সঙ্গে একাকার হয়। লেখক নিগৃহীত তিতাসপাড়ের মানুষের জন্মের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন :
“সে দেখিয়াছে কত শিশুর জন্ম, দেখিয়াছে আর ভাবিয়াছে। ভাবী নিগ্রহের নিগড়ে নিবদ্ধ এই অজ্ঞ শিশুগুলি জানে না, হাসির নামে কত বিষাদ, সুখের নামে কত ব্যথা, মধুর নামে কত বিষ তাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।”
তিতাস একটি নদীর নাম এবং মানবিক উত্থান-পতনের এক সার্বজনীন ইতিবৃত্ত
তিতাস নদীর তীরের কৃষিজীবী
তিতাসের তীরে জেলে ছাড়াও আছে কৃষিজীবী মানুষের বাস। লেখক তাদেরও জীবন-জীবিকার জটিলতাকে ধারণ করেছেন সব্যসাচী শিল্পীর তুলিতে। উপন্যাসের প্রথম পর্বেই গৃহস্ত জোবেদ আলীর বাড়িতে কাজ করতে আসা দু জন মুনীশের পারিবারিক কষ্টের বিবরণের মধ্যে সে-বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সীমাহীন না পাবার যন্ত্রণায়ও তাদের বিবেক জাগ্রত থাকে সবার ওপরে। এজন্যই খাওয়ার পর গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বন্দেআলী তার পরিবারে অভুক্ত থাকা স্ত্রীর কথা ভাবে। ‘ভাই করমালী নিজে ত খাইলাম ঝাগুর মাছের ঝোল। আমার ঘরের মানুষের একমুঠ শাক-ভাত আজ জুটল নি, কি জানি?’
ভূমিহীন চাষীর কাছে প্রেম-ভালোবাসা
নিম্নশ্রেণীর মানুষের আরেকটি সংকট উপস্থিত হয় আর তা হলো বন্দেআলীর দৃষ্টিতে করমালীর প্রেমিক মন নিষ্ঠাহীন। কারণ তার কাছে এসব পারিবারিক প্রেম-ভালোবাসার কোন স্থান নেই। বস্তুত ভূমিহীন চাষীর কাছে এসবের কোনো দাম নেই। জীবনে ভাল থাকা যাকে বলে তারা তার অংশীদার নয়। এজন্যই লেখক বলেন :
“জীবনে যদি বসন্ত আসে তবেই এসবের দাম চোখে ধরা পড়ে। তাদের জীবনে বসন্ত আসে কই।”
অন্তর্জীবনের যন্ত্রণা
দেখা যায় নারীর অন্তর্জীবনের যন্ত্রণাও তিতাসের পাড়ে আঁছড়ে পড়ে। বস্ত্রাচ্ছিত নৌকায় চড়ে ‘যে বউ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল’। শত বেদনার ইতিহাসে অঙ্কিত তাই তিতাসের বুক।
অভিধানের পাতায় তাই তিতাস নদীর নাম না থাকলেও এর অন্তর্গত সুখ-দুঃখের ইতিহাস, ‘সত্যের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মত স্পর্শপ্রবণ’। ফলে তিতাস নদী নিজেই রচনা করে চলে এক অনন্য ইতিহাস। সে ইতিহাস বাংলাদেশের নদী বিধৌত শত শত জনপদের নিম্নজীবী মানুষের বাঁচা-মরার ইতিহাস। তাই আঞ্চলিক কাহিনী-কাঠামোতেও সে ধারণ করে মানবিক উত্থান-পতনের এক সার্বজনীন ইতিবৃত্ত।
তিতাস নদীর পাড়ের মালোসম্প্রদায়
‘ধনুকের মত বাঁকা’ তিতাসের তীর ঘেঁষে দক্ষিণপাড়ায় ছোটো ছোটো ঘর বেঁধে বাস করে মালোসম্প্রদায়। লেখকের বর্ণনায় :
“ঘাটে বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তক্লি- সুতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।”
নদীভিত্তিক সমাজের পরিবেশগত বাস্তব পরিচয়ে চিহ্নিত এই মালোপাড়া। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের দ্বিতীয়পর্ব ‘প্রবাসখণ্ড’ এভাবেই মালোদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দৃশ্যপট উন্মোচন করে। সঙ্গে সঙ্গে মালোজীবনের গভীর সত্য ও বৃহত্তর সংগ্রামী জীবনের ইঙ্গিত এ-পর্বকে বিশিষ্ট করে তোলে। কিশোর, বাসন্তী ও সুবলকে ঘিরে কারুণ্যময় যে জীবন তা এখানে আভাসে প্রকাশিত।
বাসন্তীর জন্য সুবল-কিশোর দু জন মিলে ‘চৌয়ারি’ বানালেও সুবলকে তার অধিকার ছেড়ে দেয়া কিশোরের পরিণামী বাস্তবতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। পরবর্তী কালে বাসন্তীর মনে কিশোরের জন্য সে অনুভবি সত্তার আবিষ্কার পাগল কিশোরের প্রতি ভাবনায় ও অনন্তের মার প্রতি বাসন্তীর তীব্র মমত্ববোধে ভিন্নতর এক বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। তবুও এ-উপন্যাসে প্রেম কোনো মুখ্য ব্যাপার নয়। জীবন-সংগ্রামে নিয়ত যোদ্ধা মালোদের গভীরতম এক সত্যের কথাই এ-উপন্যাস উচ্চকিত। জেলেজীবনের কর্মকঠোর মলিন এক বাস্তবতা অন্যদিকে উৎসব মুখরতায় শান্ত-নিরপদ্রুপ জেলেজীবনে কিঞ্চিৎ আনন্দপ্রাপ্তির কথা তাই ‘প্রবাসখণ্ড’ পর্বে অঙ্কিত হয়েছে।
সুবল কিশোরদের লেখাপড়ার পাট চুকে যায় বাল্য বয়সেই। অন্যের নৌকায় জীবিকারোহনের জন্য প্রবাসযাত্রা তাদের এ-পর্বেই। মালোজীবনের নিয়ত সংগ্রামের শুরুও এখান থেকে। নৌকা চালনার পথে ভৈরবে গিয়ে সন্ধ্যা হলো রাত্রির আশ্রয়প্রার্থী তাদের চোখে ধরা পড়ে মালোজীবনের আরেক বাস্তব। তারা আবিষ্কার করে যান্ত্রিক পৃথিবী ও নাগরিক জীবনের সুবিধাপ্রাপ্ত ভৈরবের মালোরা তাদের চেয়ে অগ্রগামী। তাদের না পাবার কথা নিচের বাক্যগুচ্ছে স্পষ্ট হয় :
“এ গায়ের মালোরা গরীব নয়। বড় নদীতে মাছ ধরে। রেলবাবুদের পাশে থাকে। গাড়িতে করিয়া মাছ চালান দেয়। তারা আছে মন্দ না।”
ভৈরবের মালোসমাজে দর্শনীয় এ-অবস্থার পেছনেও যে একটি অশুভ শক্তির অপতৎপরতা আছে তা বুঝতে বাকি থাকে না। নাগরিক সভ্যতা কর্তৃক গ্রাম বিনাশের যন্ত্রণা এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি নষ্ট হবার কষ্ট সুবল, কিশোর আর তাদের নৌকার সঙ্গী বৃদ্ধ তিলকও বুঝতে পারে। মালোদের অনেক জায়গা রেল কোম্পানি নিয়ে নিয়েছে। ফলে ‘বৃহত্তর প্রয়োজনের পায়ে ক্ষুদ্র আয়োজনের প্রয়োজন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।’ তারা এ-সত্য বুঝতে পারে বলে সুবলের ভাবনায় উঠে আসে নাগরিক ডেভেলপমেন্টের এক অন্তর্বাস্তব। সুবল তাই বলে :
“কিশোর দাদা ভৈরবের মালোরা কি কাণ্ড করে জান নি? তারা জামা জুতা ভাড়া কইরা রেল কোম্পানির বাবুরার বাসার কাছ দিয়া বেড়ায়, আর বাবুরাও মালোপাড়ায় বইয়া তামুক টানে আর কয়, পোলাপান ইস্কুলে দেও- শিক্ষিৎ হও শিক্ষিৎ হও।”
এই শিক্ষিত হয়ে ওঠার পেছনে জীবনের অপ্রাপ্তি আর অনাদায়ী এক চরম বাস্তবতা সঙ্গে সঙ্গে আঘাত হানে বৃদ্ধ তিলকের বুকে। কারণ সে জানে বৈষম্য ঘুচানোর অর্থ শুধু শিক্ষিত হওয়া নয়। মনুষ্যত্ববোধের অঙ্কুর ঘটাতে হয় মানুষের সজীব হৃদয়েই। তাই সে ক্ষেপে উঠে বলে- ‘হ শিক্ষিৎ হইলে শাদি সম্বন্ধ করব কি না। আরে সুবলা তুই বুঝবি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায় আর চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর।’ কিশোরের আরেকটি রসিকতা সমাজকৃত বৈষম্যের মূলে আঘাত করে। সে হেসে বলে, ‘না তিলকচাঁদ না। চোখ রাখে বড় মাছের উপর।’
জেলেরাই পায় না বড়ো মাছের স্বাদ
প্রবাসযাত্রা শেষে উজানিনগরের খলায় বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে উপস্থিত হয় সুবল-কিশোর। এখানে যা রান্না হয়েছে সব বড়ো মাছের। মোড়ল ও মোড়ল গিন্নীর যত্ন সত্ত্বেও কিশোরদের মনের গোপন অথচ নির্মম সত্যের এক অনুভবী ভাষা লেখক দান করেন। তারা জেলে হলেও বড়ো মাছের স্বাদ জীবনে খুব একটা পায় না। বড়ো মাছ তাদের জালে ধরা পড়লেও পয়সার জন্য বেঁচে দিতে হয়। অথচ জলই তাদের জীবন-মরণ, জীবনের অন্যতম রোমান্সও এই নদীর রহস্যে উৎপাদিত।
ধান থাকলেও চাষীদের জোটেনা গামছা
মালোজীবনের রূপ ও তার জটিলতাকে লেখক সরল ভাষিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। জেলেদের পাশাপাশি যে চাষীরা এখানে বাস করে তারাও জীবন-জীবিকার জটিলতায় আক্রান্ত। লোন কোম্পানির টাকা নিয়ে তারা কখনোই শোধ করতে পারে না। ঘরে ধান থাকলেও তাদের কোমরে একখানা গামছা জোটে না। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক চাষীই জমি পর্যন্ত বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়। জোঁয়ার-ভাটার কারসাজিতে জলের ওপর তাদের ভরসা কম। ফলে মাটিই তাদের কাছে খাঁটি। আর এজন্য বাহারুল্লাকে রামপ্রসাদ শোনায়- ‘মাটির সাথে সম্বন্ধ ছাড়া মানুষের জীবনের কোন বিশ্বাস নাই, বাহারুল্লা ভাই।’ মালোপাড়ার কৃষকশ্রেণির মাটির অবলম্বনটুকু থাকলেও জেলেজীবনে তা-ও নেই। তারপরও জেলেজীবনের সঙ্গে চাষীদের আর্থ-সামাজিক দৈন্য, তাদের মধ্যে সমধর্মিতা ও সহমর্মিতার জায়গাটি লেখক আবিষ্কার করেন।
‘রাতের ঝড়ে পাখির যে ডানা ভাঙ্গিল, সে ডানা আর জোড়া লাগিল না।’
সুবল ও কিশোর এ দুই চরিত্রে কিছুটা বৈপরীত্যের চিহ্ন আছে। কিশোর স্বভাবগতভাবেই সূক্ষ্ম শিল্পবোধসম্পন্ন অন্যদিকে সুবলের ভেতরে যৌবনের উত্তাপ কিছুটা পরিমার্জনাহীন। উজানিনগরের প্রবাসে প্রেমের দেবতা তাই কিশোরের জন্যই ফাঁদ পাতে। পঞ্চদশী এক মেয়ের সঙ্গে কিশোরের ভাব তৈরি হয়। মোড়ল গিন্নির হাত থেকে ফুলের মালা নিয়ে তাদের মালাবদল করা হয়। অন্যদিকে বাসন্তীর দায়িত্ব সুবলের হাতে ছেড়ে দেয় কিশোর। কিন্তু নতুন স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে না করতেই কিশোরের জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ যন্ত্রণার অগ্নিবাণ। রাতের অন্ধকারে ডাকাত দল নিয়ে যায় তাদের মুনাফার দুইশত টাকা। স্ত্রীকে হারায় কিশোর। সুবল ও তিলকের আপ্রাণ চেষ্টায় নৌকার গতি সামলে নেয়া গেল কিন্তু কিশোর হলো পাগল। লেখকের ভাষায়- ‘রাতের ঝড়ে পাখির যে ডানা ভাঙ্গিল, সে ডানা আর জোড়া লাগিল না।’ লেখকের এ-কথা ইঙ্গিতময়; কিশোর ও অনন্তর মায়ের পরিণামী বাস্তবতার নির্দেশক।
নিত্যানন্দ আর গৌরাঙ্গের আশ্রয়ে থাকার চার বছর পর ‘নয়াবসত’ পর্বে অনন্তের মা কিশোরের খোঁজে বের হয়। এতদিন পর কিশোরকর্তৃক তাকে না চেনার ভীতি তখন তার বুকে।
“মনে পড়ে নৌকাতে যখন মাচানের তলায় ছিলাম বন্দী, তার বন্ধু আসিয়া খাওয়াইত, কিন্তু সে থাকিত দূরে দূরে। বন্ধুকে সে বলিয়াছিল, আমি দেখিতে কেমন সে তা ভুলিয়াই গিয়াছে। আমার নয় চাহিতে বাধা, তার চাহিতে বাধাটা ছিল কোথায়। এত ভাল যার মন, সেকি এখনো দেখিলে চিনিতে পারিবে?”
আসলে সমাজ-সংস্কারের ভয় ছিল অনন্তের মার মনে। আবার ডাকাত দল যাকে অপহরণ করেছিল তাকে সে বিশ্বাস করবে কীনা এ-নিয়েও সংশয় ছিল। ঘাটে নৌকা ঠেকবার কিছুক্ষণের মধ্যে তার চোখে ভাসল করুণ এক দৃশ্য। এক পাগলকে দুই বুড়োবুড়ি টানাটানি করে ঘাটের দিকে নিয়ে আসছিল। জলে নামবে না বলে বৃদ্ধ লোকটি প্রথমে তাকে শাস্তি দিল আর উচ্চস্বরে কান্না করে গলাগলি ধরে পানিতে নামল। কিন্তু বুড়ির চোখে কোন অশ্র” ছিল না। মায়ের চরমতম মানসিক যাতনার ভাষাকে লেখক নিরবতা দিয়ে ঢেকেছেন- ‘সব কান্না তা শুকাইয়া গিয়া বুঝিবা জমাট বাধিয়াছে।’ হতভাগ্য সন্তানের কষ্ট দেখে অনন্তের মা আতঙ্কিত; তাই অনন্তকে বুকে চেপে ধরে সান্তনা খোঁজে। কিন্তু অনন্ত কি শেষ পর্যন্ত পারবে মায়ের আঁচলের তলার নিবিড় শান্তিটুকু অনুভব করতে? ভাগ্য তাকে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে ঠেকাবে তা এক বিপর্যস্ত মানুষের চরম বেদনায় সমাহিত।
অনন্তর মা বাসন্তীর ঘরভুক্ত
কালোর মা কম দামে একখানি ভিটে ছেড়ে দেয়। সেখানে ওঠে অনন্তর মার ঘর। বর্ষিয়সী রঙিনী মহিলারা অনন্তের মার সঙ্গে দেখা করতে আসে কিন্তু তারা তার মন পায় না। কারণ ঠাট্টা-তামাশা করা সে ভুলে গিয়েছে। তারা মনে করে, ‘এ নারী অনেক দূরের। এইত একমুঠা মেয়ে তাকেও দলে পাইবে না। এত দেমাক।’ কালোর মা তাকে আশ্রয় দিলেও দুঃখের ভাগী হয় না। কিন্তু অনন্তের মার মনের ভাষা বুঝল যে নারী সে আর কেউ নয়- সুবলার বউ বাসন্তী। অল্প বয়সে বিধবা এই নারীর সঙ্গে তিতাসের ঘাটে তার সাক্ষাৎ হয়। তার সমবেদনার নিঃশ্বাস অনন্তের মাকে মুগ্ধ করে। লেখকের ভাষায়- ‘হরিণী যেমন নিজের কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করে, সুবলার বউয়ের আবির্ভাবও অনন্তের মা তেমনি করিয়া গ্রহণ করিল।’ ভারতের বাড়িতে সভা বসলে বাসন্তী তাকে নিজের ঘরের মানুষ করে নেয়। কোনো কোনো আদিবাসী সমাজের মত মালোপাড়ায় নতুন কোন ব্যক্তি এলে তাকেও কারো না কারো পরিবার তথা সমাজে দলভুক্ত হয়ে থাকতে হয়। অনন্তর মাও তাই বাসন্তীর ঘরভুক্ত হয়ে বাস করতে থাকে।
মালোজীবনের শত দারিদ্র্য আর যন্ত্রণা
বহুভঙ্গিম সমাজের বাস্তবতা থেকে মালোসমাজ দূরে নয়। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে দেখায় যায় প্রতিষ্ঠাহীন মালোজীবনের শত দারিদ্র্য আর যন্ত্রণা তাদেরকে সভ্যতার অন্তরালবর্তী মানুষ করে রাখে। শিক্ষিত মানুষদের প্রতি তাই তাদের কোন আস্থা নেই। কিশোর যখন উজানিনগরে তখন তার হবু আত্মীয়কুটুমদের একজন বলেছিল- ‘আপনার দেশ নাকি সুদেশ। দেখতে ইচ্ছা করে। কায়স্থ আছে, ব্রাহ্মণ আছে, শিক্ষিত লোক আছে। বড় ভালো দেশে থাকেন আপ্নেরা।’ তখন কিশোরের অস্ফূট অভিব্যক্তিকে লেখক নিজে প্রকাশ করেন- ‘শিক্ষিৎ লোকের দেশে থাকার যে কি কষ্ট, আর এদের মত দেশে থাকার যে কি সুখ, এ কথাগুলি যুক্তিপ্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিবার কিশোরের সময় নাই।’ শিক্ষিত মানুষের প্রতি বিশ্বাসহীনতার বিষয়টি কৃষক কাদির মিয়ার ভেতরেও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষিত করে তুলবার জন্য কৃষক ছাদির মিয়া তার পুত্র রমুকে মক্তবে পড়াতে চাইলেও দাদা কাদির মিয়া বাধ সাধে।
“…কাদির বলিল, ‘দে, তোর পুতেরে মক্তবে দে, কিন্তু কইয়া রাখলাম, যদি মিছা কথা শিখে, যদি জালজুয়া চুরি শিখে, যদি পরেরে ঠকাইতে শিখে, তবে তারে আমি কিছু কমু না, শুধু তোমার মাথাটা আমি ফাটাইয়া দিমু ছাদির মিয়া।”
সমাজের শিক্ষিত মানুষগুলোর প্রতি কৃষক কাদিরের এ-অনুভব ঈর্ষা নয়। সে তার ক্ষুদ্রগণ্ডি থেকেও নিজের যন্ত্রণা আর জীবনাভিজ্ঞতার প্রবল অনুভবের আলোকে সভ্য মানুষের এক ন্যাক্কারজনক অস্তিত্ব টের পেয়েছে। তাদের সম্পর্কে যে পরিচয় সে পেয়েছে তাকেই ধর্তব্য বলে ভেবে একটি সাধারণীকরণ করেছে। শিক্ষিত মানুষের ঘুষ খাওয়া, দুর্নীতি করার বিষয়টি তার আত্মীয় বেয়াই তথা ছেলের শ্বশুর মুহুরিকে সামনে এনেছে। বেয়াই মুহুরি অসৎ মানুষের প্রতিনিধি তাই কাদিরের কাছে শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জাল জুয়াচোর নষ্ট খল। তাই নাতিকে মাঠে পাঠিয়ে নিরক্ষর করে রাখতেও সে রাজি আছে কিন্তু ইস্কুলে পাঠাতে রাজি নয়। তার কথায় :
আর ইস্কুলে পাঠাইলে, তোর শ্বশুরের মত মুহুরী হইতে পারিবে আর শাশুড়ির বিছানায় বউকে ও বউয়ের বিছানায় শাশুড়িকে শোয়াইয়া দিয়া দুরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুণিতে পারিবে। কাজ নাই বাবা অমন লেখাপড়া শিখিয়া।
লেখাপড়া জানা মানুষগুলোর প্রতি এই অবিশ্বাস আর সন্দেহের বিষবাষ্প রাষ্ট্র ও সমাজের কোন এক গোপন স্থানে আঘাত হানে। বর্ণমালা চেনা মানেই মানবিক হয়ে ওঠা- এমন নীতির বির”দ্ধবাদিতা এদের তীব্র রোষের ভাষায় রূপান্তরিত হয়।
ঘরের মালিক হলেও জমির মালিক নয়
আন্তরিকতা নয় বরং বুদ্ধির জোরে যারা জিতে যায় তারাই মালোসমাজে প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতের বাড়ির সভার মধ্যেও একটি চাপাগুঞ্জনে সে-সত্যের ইঙ্গিত মেলে। লেখকের ভাষায়- ‘প্রতিষ্ঠাহীন জীবনের সাহসের স্বভাব-সুলভ অভাবই এদেরকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে।’ তাই মালোরা ঘরের মালিক হলোেও মাটির মালিক তারা নয়। প্রজা উচ্ছেদ হলোও তাই নতুন প্রজা আসে। জমিদাররা সংখ্যায় কম কিন্তু তারাই উৎপীড়ক:
“তারা সত্য নয় বলিয়াই তারা সংখ্যায় কম। মানুষের মধ্যে তারা ব্যতিক্রম। রায়তেরাই সত্য। তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাটির মালিক হয় তারাই। কাগজপত্রের মালিক নয়, বাস করার মালিক। সেইরূপ তিতাসের মালিক জেলেরা। কাগজপত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা।”
ধুতির দামে বিক্রি হয় মালো সমাজের মানুষ
একসময়ের জমিদারী ব্যবস্থায় বছরে একবার প্রাচীনকালের নিয়মে মালোদেরকে দশভার মাছ দিতে হতো। কিন্তু মৎস্যপ্রাপ্তি অনিশ্চিত বিষয় হওয়ায় সকলে যার যার ‘মাথট’ তুলে রাজার কাছে পৌঁছে দেবে এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়। অন্যদিকে সমাজ পরিবর্তনের সূত্রেই তৈরি হয় বাজার-ব্যবস্থা। শহরে মাছ বিক্রেতাদেরকে নতুন মাশুল গুণতে হয়। আনন্দবাজারে মাছ বিক্রি করতে আসা মালোদের কাছ থেকে ভার পিছু দু আনা করে মাশুল চায় জমিদারের লোকেরা। ফলে পুঁজির নতুন আগ্রাসন বেড়ে চলে বাজার-ব্যবস্থাকে ঘিরে। পুঁজির অসুস্থ প্রতিযোগিতার কালো ছায়াবাজির শিকার হয় মালোপাড়ার দরিদ্র মানুষ। জগৎবাবু ও আনন্দবাবু শহরের দুই গণ্যমান্য জমিদার নিজেদের নামে বাজার বসায়। পুঁজির অন্তর্গ্রাসী ক্ষমতায় মালোসমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বিক্রি হয় পঁচিশ টাকা নগদ আর একটি ধুতির দামে। আনন্দবাবুর বাজার ফুলে ফেঁপে ওঠে। আনন্দবাবু আজ না থাকলেও তার লোকেরা মালোদের কাছে খাজনা চায়।
আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিবাদী মালোসমাজ
আত্মমর্যাদাবোধ গোকর্ণঘাটের মালোদেরকে প্রতিবাদী করে তোলে কখনো কখনো। তাই যুগযুগ ব্যাপী শোষণে জর্জরিত মালোসমাজের মানুষ এখন আর নির্বিচারে সব কিছু মেনে নিতে চায় না। অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী আর জমিদার বাবুকে তারা তাদের আবেগসুলভ প্রতিবাদ জানায় : “শুন বেপারী, বাবুরে সাফ সাফ কইয়া দিও, মালোরা মাছ বেঁচতে কোন সময় মাশুল দেয় নাই, দিবেও না। জায়গা দেউক আর না দেউক। মালোরা বাজার জমাইতে যেমুন জানে, ভাঙতেও জানে। তারা যেখানে যায়, আ-পথে পথ হয়, আ-বাজারে বাজার হয়।”
আত্মবিক্রয় এবং মালোসমাজ ধ্বংসের একজন অনুঘটক
মালোপাড়ায় তামসীর বাপই কেবল বাজারের কায়েতদের সঙ্গে মিশে মালোপাড়ার মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিতে আঘাত হানে। তামসীর বাপ নিজেও সে-বিষয়টি বুঝতে পারে। তামসীর বাপকে বাজারের কায়েতরা খাতির করলেও এ-কথা সত্য যে, মালোদেরকে তারা কখনোই আপন করবে না। নিজেকে অপরাধী করে নিজের মনেই তার সে-ভাবনার উদ্গীরণ হয় : “সত্যই ত, পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। তারা আমার কে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনো জিনিস ছুঁইলে তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসিতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে।”
আত্মবিক্রয়ের স্বার্থে তাই দুষ্ট খল হলোও তামসীর বাপের মধ্যেও এক ধরনের শুভবোধ জাগ্রত হয়। উপন্যাসের শেষপর্য়ন্ত অবশ্য তা টিকে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে মালোসমাজ ভাঙনের জন্য সে একজন অনুঘটক। তার বাড়িতেই বাজারের কায়েতদের আড্ডা বসে যা মালোসমাজের বন্ধনের মূলে আঘাত করে। গভীর এক আন্তরিকতার বন্ধন মালোপাড়ার মানুষদেরকে পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত করে রেখেছিল। যতদিন তারা একে অপরেরর প্রতি সহমর্মী থাকতে পেরেছে ততদিন মালো সমাজে ভাঙন দেখা যায়নি। কায়েতরাই তাদের সর্বনাশ করে। তাই শিক্ষিত মানুষ সম্পর্কে নিগৃহীত মালো-হৃদয়ে ঘৃণার ভ্র”কুটি সঞ্চারিত হয়। নিম্নশ্রেণির মানুষের উচুশ্রেণির মানুষ সম্পর্কে উষ্মার ভাষাকে অদ্বৈত ধারণ করেন :
“এরা মালোদেরকে কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত ধুতি-চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁয়ারও অযোগ্য। মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।”
কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না।
অদ্বৈতর মল্লবর্মণের আত্মার প্রতিফলনই যেন এ-ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বহমান সুদূর অতীত থেকে সমাজ-বৈষম্যের যে পাকাপোক্ত ভিত গড়ে উঠেছে সেখানে ধূলির ঝড়ের মত কাঁপন লাগে। অস্পৃশ্য মানুষের মানবিক যাতনা সশব্দে উচ্চারিত হয়। দয়ালচাঁদ নিগৃহীত মালোসমাজের আরেকটি নির্মম সত্যের দুয়ার খুলে দেয়। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তামসীর বাপকে শুনিয়ে কায়েতদেরকে উদ্দেশ্য করে সে উচ্চারণ করে :
“বাজারের কাছে তোমার বাড়ি। বাজারের কায়েতরা তোমার বাড়িতে আসিয়া নাকি তবলা বাজায় আর মেয়েদের দিকে নজর দেয়। ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙা তক্তা। তুমি রূপার হুকোতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কল্কেখানা।”
মাছের মতো জন্ম, আবার মাছের মতোই মৃত্যু
মানুষের জীবনে জন্ম মৃত্যু বিবাহ- এ-তিন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এই তিন বিষয়ে মালোরা সামর্থ্য থাকলে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করে না। তবে তাদের সবার জীবনে অবশ্য এমন সৌভাগ্য আসে না। কখনো মৃত্যুর দেবতা আগেই এসে মালোশিশুর জীবনপ্রদীপ নিভে দেয়। মাছের ঝাঁকের মতই তারা জন্মায় আবার মাছের পোনার মতই কেউ কেউ অজান্তে হারিয়ে যায়। তরুলতার শুষ্ক পত্রগুচ্ছের মতই মালো-প্রজন্মের পরিণতি। লেখক তাই বলেন :
“একবার যে জন্মিয়াছে সে একদিন মরিবেই। কাজেই যে ঘরে মানুষ আছে মৃত্যু সে ঘরে ঘটিবেই। কিন্তু ঘরে মানুষ আছে বলিয়াই এবং সে ঘরে মৃত্যু একদিন ঘটিবে বলিয়াই জন্ম ও বিবাহও সে ঘরে ঘটিবেই এ কথার অর্থ হয় না।”
পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা
মালোপাড়ার সবশিশু ভাগ্যবান না হলেও সম্পন্ন কালোবরণের ঘরে জন্মানো শিশুদের ‘অন্নপ্রাশন’ হয় অনেক জাঁকজমকভাবে। অর্থভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে আরেকটি নগ্ন সত্য এখানে প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে- পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আধিপত্য। পুরুষ ও নারী শিশুর মধ্যেও তা ব্যবধান তৈরি করে। ফলে সন্তান জন্মানোর সময় তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়- ‘ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হলে তিন ঝাড়।’
বিশ্বাস সংস্কার
জেলেজীবনের বিশ্বাস সংস্কার তথা জীবনাচারের অনেক গভীর সত্যের ইঙ্গিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ দিয়েছেন তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের ‘জন্ম মৃত্যু বিবাহ’ নামক এ-পর্বে। ছ দিনের দিন শিশুর ঘরে দোয়াত কলম দেয়া হয়। রাতে চিত্রগুপ্ত এসে দোয়াত থেকে কালি তুলে কলম দিয়ে শিশুর ভাগ্যলিপি লিখে যায়। সুবিধা-বঞ্চিত মালোরা অবচেতনে সভ্য হবার অর্থ খোঁজে। তাই মনে মনে শিক্ষিত মানুষকে ঘৃণা করলেও শিক্ষিত হবার মূল্য তারা বোঝে। অন্যদিকে ভাগ্য তাদেরকে প্রবঞ্চিত করলেও ভাগ্যকে তারা শিশুর কপালে কলমের আঁচড়েই ধারণ করে। জীবিকার অনিশ্চায়ক এক জীবনের শিকার হলেও শিশু জন্মের অষ্টম দিনের ‘আট-কলাই’ উৎসবে তারা খই-বাতাসা বিলায়। তের দিনের দিন তারা পালন করে ‘অশৌচ অন্ত’। এদিন পরিচ্ছন্নতার আয়োজন করে মালোরা। দু দিন পরে পালন করা হয় ‘স্নানযাত্রা’। গান গেয়ে তিতাস ঘাটে গিয়ে তারা নদীকে তিনবার নিজেরা প্রণাম করে। তারপর তারা ছেলেকেও প্রণাম করায়। অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ছেলের মাথা ধোয়ান হয়। তিতাস মালোপাড়ার মানুষের কাছে শুধু একটা নদী নয়, বিশ্বাসবদ্ধ জীবনের অন্যরকম চালিকাশক্তিও। কেননা তিতাসের তীরেই তাদের বাঁচা-মরার ইতিহাস সঞ্চিত। তিতাসের পানিতে নেমে মিথ্যে বলাও তাই তাদের রীতিবিরুদ্ধ।
সরলমনা সুবল, মালিকশ্রেণি এবং বাসন্তী
জিয়লের ক্ষেপ দিতে গিয়ে সুবলের মৃত্যুর খবর লেখক এ-পর্বে স্পষ্ট করেছেন। একদিকে কালোবরণের বাড়িতে সন্তান জন্মের উৎসব অন্যদিকে তারই নৌকার তলার সুবলের মর্মান্তিক মৃত্যুকে তুলে ধরায় উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাহীন ব্যবধানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালোবরণের নৌকা তীরের ধাক্কা সামলাতে পারবে না বলে আরো পাঁচজনকে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ তারা সবাই জলে ঝাঁপ দিয়ে নৌকা রক্ষা করবে এই অভিপ্রায়ে) সুবলই প্রথমে নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু নৌকার তলায় তার বুকের পাঁজর ভেঙে হয় মর্মান্তিক মৃত্যু। সরলমনা সুবলের মৃত্যুতে মালিকশ্রেণির প্রতিনিধি কালোবরণের কোন যায় আসে না। এতে ক্ষতি হয় বাসন্তীর কিংবা সুবলের ভাগ্যহীন বৃদ্ধ পিতা গগণ মালোর। সুবলরা যেমন নৌকার মালিক হয়নি তার বাবা গগন মালোও কোনদিন নৌকা বা জালের মালিক ছিল না। সারাজীবন পরের নৌকায় জাল বেয়েই তার দিন কেটেছে। সুবলের অকাল মৃত্যু নিয়ে তাই লেখকের অভিব্যক্তি:
মালিকেরা চতুর মানুষ তারা নিজেরা কিছু না করিয়া, যাকে জন খাটাইতে নিয়াছে বিপদ আপদেও কাজগুলি তাকে দিয়াই করায়।
নিম্নশ্রেণির মানুষকে জীবন দিয়ে হলেও যেখানে শোধ করতে হয় মালিকশ্রেণি সেখানে থাকে নিষ্কন্টক। এই সরলতম সত্যের বাস্তবায়ন সুবলের জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। পুঁজির কাছে কপর্দকশূন্য হাতের চরম পরাজয়ও এখানে ঘনীভূত। কারণ সুবল প্রথমে কালোবরণের নৌকায় ভাগীদার হবার প্রস্তাব করলেও তার সে কথা রাখা হয় না। পুঁজিহীন সুবলকে চাকর জ্ঞান করাই তখন কেবল নিয়ম। জেলে ছাড়াও কৃষকশ্রেণীর মানুষ অল্পদামে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাই দেখা যায় মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা সারা পৃথিবীতেই সক্রিয়। ‘রামধনু পর্বে’ কাজেই চরের জমিতে রোপিত আলু বিক্রি করতে চায় না কৃষকরা। তাদের কাছে-
“মাছ- বেপারীরাও এই রকম। জাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জায়গায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।”
সুবলের বাপ গগন মালোর কাছেও এ-নিয়ম অনুপেক্ষণীয়; তাই তার নিজের নৌকা-জাল হয় না। সুবলের মা সবসময় তাকে ভর্ৎসনা করে বলত- ‘এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কতদিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারী কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেনে?’ কিন্তু মালোপাড়ায় শ্রম ও শক্তির ক্ষয়ে বুড়িয়ে যাওয়া মানুষেরও জীবনের ঘানি টানা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকে না। সুবলের মৃত্যু তার পরিবারের সব মানুষের ক্ষতি বয়ে আনে। কিন্তু নির্লিপ্ত সমাজ তা চেয়ে চেয়ে দেখে।
সুবলের মৃত্যু বাসন্তীর মনে পৃথিবীর নিষ্ঠুর মালিক শ্রেণি বিরুদ্ধে ঘৃণার চরম ভাবটি জাগ্রত রাখে। চার বছরে অনেক কিছু ভুললেও মনিবের অসঙ্গত আদেশের কাছে অসহায় স্বামীর নিদারুণ মৃত্যু তার মনে পাথর চাপা কষ্ট তৈরি করে। কালোবরণের প্রতি সে থাকে ক্ষমাহীন, জটিল ক্রোধাক্রান্ত। সুবলের মৃত্যুতে-
“বাসন্তীর হাতের শাখা ভাঙ্গিল, কপালের সিঁদুর মুছিল। কিন্তু জাগিয়া রহিল একটা অব্যক্ত ক্রোধ।”
বাসন্তী আর অনন্তর মা
বাসন্তীর মনের তলায় লুকিয়ে রাখা যন্ত্রণায় সমাজ-বিদ্বিষ্ট। আবার তার মধ্যেই নারীত্বের সহজাত মহিমা কিংবা বাৎসল্য ঘিরে থাকে অনন্ত ও তার মাকে ঘিরে। বাসন্তীই তার অন্তরাত্মা দিয়ে টের পায় অনন্তর মায়ের ভেতরের নারীটিকে। তাই তার দুঃখের সঙ্গে সহমর্মী হবার বাসনাও তার থাকে জাগরূক। চিরদুঃখী অনন্তর মার জন্য নিজের মায়ের কাছে ময়নার নামে মিথ্যে ছলনা করতেও তার বাধে না। কারণ সে সততায় মহীয়ান; নিজের আত্মবিশ্বাসের কাছে মাথানতকারী। এ-পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই বাসন্তীর পক্ষে অনন্তর মাকে আবিষ্কার।
কিশোর ও অনন্তর মায়ের মৃত্যু
বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে লেখক মহান করেন। প্রথমবার হোলির উৎসবে আবিরে রাঙানো ছিল কিশোর ও অনন্তর মা। এবার চরম মৃত্যুতে তারা তাদের দেনা শোধ করল আবার কোন এক হোলির আবির মাখা রক্ত রঙে। কিশোরের পাগলামী বেড়ে গেলে অনন্তর মাকে সে পাঁজাকোলা করে শূন্যে ওঠায়। অনন্তর মার বুকে মুখ ঘষতে শুর” করে সে। অনন্তর মা মূর্ছা যায়। কিন্তু হোলীর উদ্দীপনায় উত্তেজিত লোকগুলো কিশোরের পাগলামী বুঝতে পারে না। তারা না চিনে কিশোরকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়। কোনরকম রাতটা বেঁচে থেকে কিশোর পরদিন মারা যায়। চার দিনের ব্যবধানে কিশোর ও অনন্তর মা’র মৃত্যু ঘটে। অথচ ‘অনন্তর মা ভাবিতেছে অন্য কথা। তাদের প্রথম প্রেমাভিষেকের দিনটিকে সে কিভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে। সে পাগলকে এমন রাঙানো রাঙাইবে যে, তাতে করিয়া তাদের সে দিনের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিবে, তার পাগলামী সে নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রেমের দৃষ্টিতে তার প্রেয়সীর দিকে নয়নপাত করিবে।’
অনাথ অনন্ত
বাবা-মায়ের করুণ মৃত্যুতে অনাথ রয়ে গেল অনন্ত। বাবার স্বাদ তার কোনদিনও পাওয়া হয়ে ওঠে না। এই পাড়ার সমবয়সী অনেকেই তার মতো পিতৃহীন নয়।
“বাপ নামক পদার্থটা যে কি, অনন্ত তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। এই পাড়ার সমবয়সী অনেক ছেলেরই বাপ নামক একটি লোক আছে। বাজারের ঘাট হইতে ছোলাভাজা মটরভাজা বিস্কুট কমলা কিনিয়া দেয়। সকালে রাতের জাল বাহিয়া আসিয়া কারে বা কোলে নেয়, কারে বা চুমু খায়, কারে বা মিছামিছি কাঁদায়। দুপুরে নিজ হাতে তেল মাখাইয়া তিতাসের ঘাটে নিয়া স্নান করায়। পাতে বসাইয়া খাওয়ায়। মাছের ডিমগুলি বাছিয়া বাছিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। এসব অনন্তর একদিনের দেখা অভিজ্ঞতা নয়। অনেকদিন দেখিয়া মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, বাপেরা এইসব করে।”
অনন্তর পিতৃশূন্যতার যন্ত্রণার ভাষাকে লেখক এভাবেই রূপদান করেছেন। তার কাছে বাপের ছায়া বা প্রতিমূর্তি খুঁজতে গিয়ে সে তার আশেপাশে দেখা শিশুদের জগতে সাদৃশ্য খুঁজে পায়। পিতার স্নেহচ্ছায়া-বঞ্চিত শিশু অনন্তের কাছে বাবা মানে একটা আইডিয়া মাত্র। অন্য শিশুদের বাবার মধ্যে তার রূপ অবলোকন করে অনন্ত।
অনাথ অনন্ত এবং বাসন্তী
অন্যদিকে মাতৃহীন শিশুর জগত বেদনায় ভারাক্রান্ত। বাসন্তী মাসীর কাছে তার আশ্রয় হয়। কিন্তু মা বিহীন সংসার শীঘ্রই অনন্তকে আবার নিরাশ্রয় করে। নিত্যদিনের অভাব দারিদ্র্য দীননাথ মালোর সংসারে। বাসন্তীর মার সংসারে অনন্ত যেন একটি উৎপাত। অনন্তের প্রতি বাসন্তীর অতিরিক্ত দরদও সে সহ্য করতে পারে না। আসলে দারিদ্র্যের চরম কষাঘাতই বাসন্তীর মার নিষ্ঠুরতার পেছনে দায়ী শক্তি। দীননাথ মালোর সংসারে একদিন সে অভাবগ্রস্ততার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সেদিনের থেকে আজকের দিনে পার্থক্য নেই। বরং অবস্থা হয়েছে আরো শোচনীয়। দীননাথ মালো এখন শরীরের ভারে ন্যুব্জ। একমাত্র কন্যা বাসন্তীও স্বামী হারিয়ে আজ বাপের গলগ্রহ। বাসন্তীর জীর্ণ ঘর ঠিক করতে বুড়োর গাঁটের পয়সা সব খরচ হয়। একদিন মাছ না পেলে তাদেরকে থাকতে হয় উপোষ। অবাঞ্ছিত পোষ্য অনন্তকে তাই সে ক্রোধবশত গহীন জলে ফেলে দিতে চায়। অনন্তর এ-বাড়িতে উপস্থিতি বাসন্তীর মার কাছেও সহজ অর্থে অন্ন ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।
‘শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম।’-এ কথা বাসন্তীর মার মুখ থেকে উচ্চারিত হলেও তা অস্বাভাবিক ঠেকে না। প্রখর দারিদ্র্য তাকে স্নেহহীন করে তুলেছে। তাই অন্নগ্রহণের সময় অনন্তের পিঠে পোড়া চেলাকাঠ মারতে চাওয়া কিংবা তার মুখে জ্বলন্ত খড় গুঁজতে যাওয়ার বিকৃতিও বড় অসহায়ত্বপূর্ণ এক বাস্তবতায় রূপান্তরিত। বাসন্তীর ভেতরে এক মমতাময়ী নারীর বাস। মায়ের কথার প্রতিবাদ করে সে বলেছে- ‘ইটা মরব কোন দুঃখে? তার আগে আমি মরি, -আমি ঘরের বাইর হই!’ বৃদ্ধ দীননাথ তাকে মাছ ধরার কাজে নিতে চাইলেও কখন প্রচণ্ড ক্রোধে তার বৃদ্ধ বাবা অনন্তকে শাস্তি দিতে শুরু করে বাসন্তী এই আশঙ্কা করে। বাবা-মায়ের সঙ্গে আড়ি দিয়েও অনন্তকে সে তার কাছে রাখতে চায়। অনন্তর জন্য বাসন্তী তার মাকেও শারীরিকভাবে আঘাত করে। আবার মাকে মারার অপরাধে বাসন্তী অনন্তকে দেখে গর্জে ওঠে :
“শত্তুর তুই বাহির হ। এই ঘরে তুই ভাত খাসত তোর সাত গুষ্ঠির মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি, ঠ্যাঙের তলা পায়ের ধূলা।”
অনন্ত বুঝল মা ছাড়া কেউ আপন নয়
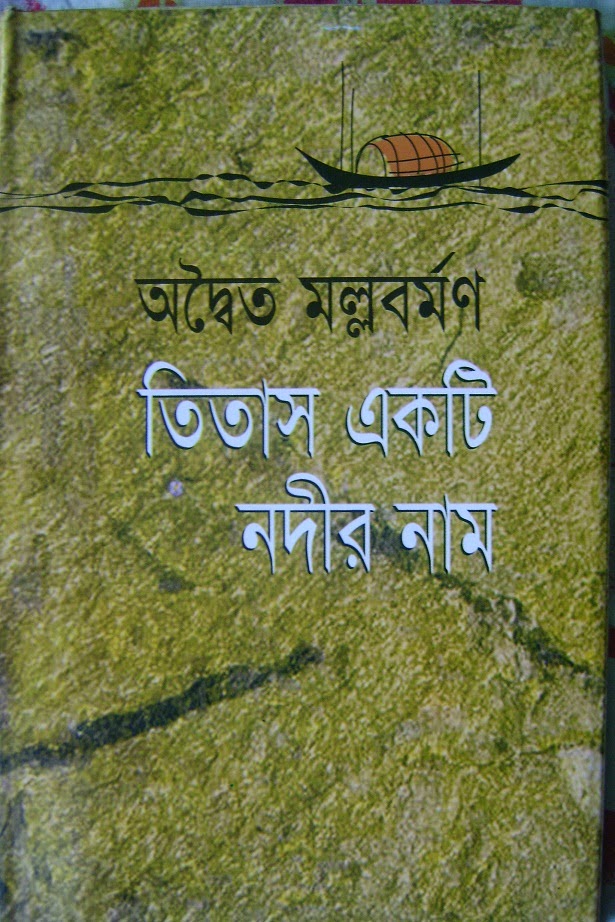
অনন্ত এখন বোঝে মা বিহীন সংসারে কেউই আপন নয়। বাসন্তীর কাছে নিগ্রহ পেয়ে অনন্তের ভালবাসার বাধন আলগা হতে থাকে। কিন্তু অনন্তের মধ্যে লেখক একটি ভাবান্তর তৈরি করেন। তাঁর উপন্যাসের কাব্যিক বয়ানের অংশ করেন অনন্তের মনের ভাবকে। তাই লেখকের স্বীয় দৃষ্টিকোণই অনন্তের মধ্যে এক ভাবপূর্ণ কবিত্ব সৃষ্টি করে। এক বাসন্তী মাসীর স্নেহের বাধন খসে গেলেও সমগ্র পৃথিবী তার কল্পনার রাজ্যে বেগবান। ‘অন্তহীন আকাশের তলায় অনন্তর আজ পরম মুক্তি। কারো পিছুর ডাকে সে আর সাড়া দিবে না।’ বাসন্তীর আশ্রয় ছেড়ে সে পায় বনমালী ও উদয়তারার আশ্রয় কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে জানে না। অনন্তর শিকড়হীন জগৎ আজ মানবিক স্নেহে সন্দিহান। অন্যদিকে যে উদয়তারার সে এখন স্নেহচ্ছায়ায় তার ভেতরেও এক বেদনাদীর্ণ নারীহৃদয় অবস্থান করে। তিক্ত বিরক্ত বাপ-মার অনাত্মীয় পরিবেশ, সন্তানহীনতার অমোচনীয় দুঃখসহ নানাবিধ ব্যথা-বেদনায় উদয়তারার হৃদয় আজ পরিপূর্ণ। কিন্তু তারপরেও তার ভেতরে রয়েছে সহ্য করবার যাদুকরি ক্ষমতা। এজন্যই তার সম্পর্কে বলা হয়েছে :
“কিন্তু বড় কঠিন এই নারী! হাস্য পরিহাসে, প্রবাদে শ্লোকে সব বেদনা ঢাকিয়া সে নারী সবসময়ে মুখের হাসি নিয়া চলে। তাহাকে জব্দ করিবে এমন দুঃখ বুঝি বিধাতাও সৃষ্টি করিতে পারে নাই।”
তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো বেদনাময় জীবনের শিকার
অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত এই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি নারীচরিত্র বেদনাময় জীবনের শিকার। পাগল কিশোরের মা থেকে শুরু করে উদয়তারা, বাসন্তী, অনন্তর মা, ছাদিরের বউ খুশি- সকলেই এক প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার দায়গ্রস্ত। তাদের মধ্যে সন্তান বাৎসল্য বা স্নেহের কমতি নেই। আবার কখনো তাদের কেউ কেউ সমাজের প্রতি খড়গহস্ত। অপমান সহ্য করতে অপারগ বলে কেউ মুখরা রমণী। রমুর দাদা কাদির ছেলের বউ খুশিকে তার বাবা সম্পর্কে কটূ কথা শোনালে সে ক্রোধান্বিত হয়। নিজের বাবা সম্পর্কে কোন মেয়েই হয়ত খারাপ কথা শুনতে চায় না। খুশির ভেতর এক বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি জেগে ওঠে :
“চোর হোক ধাওর হোক, তারইত আমি মাইয়া। বাপ হইয়া মার মত পালছে, খাওয়াইছে ধোয়াইছে- হাজার হোক, তবু বাপ। চোর হইলেও আমারই বাপ, আর কাউর বাপ না। আমি মরলে এই বাপেরই বুক খালি হইব। আর কোন বাপের বুক খালি হইব না।”
এ-কথা শোনার পর কাদিরের মধ্যে এক ভিন্ন ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। পিতার দোষে মেয়েকে দোষারোপ করা ঠিক নয় এটা ভেবেই তার মন চলে যায় তার নিজের মেয়ে জমিলার দিকে। মুহুরি বেয়াইয়ের অপত্য স্নেহের কথা ভেবেও তার হৃদয় সিক্ত হয়। বোধ হয় পৃথিবীতে বাবাদের মধ্যে অপত্য স্নেহে কোন পার্থক্য নেই।
বাসন্তীর অনুধাবন: মা একমাত্র সত্য
বাসন্তী অনন্তকে তাড়িয়ে দিলেও তার জন্যই সে উদয়তারার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। স্নেহের টানে সে পরাহত। অনন্ত তাকে ভুল বুঝলেও স্নেহের হাহাকার তাকে করে উত্তেজিত। উদয়তারাও অনন্তের প্রতি স্নেহের অন্ধ টানে বাসন্তীর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ। অনন্তকে শারীরিকভাবে আঘাত করার জন্য সবাই মিলে বাসন্তীকে নৌকার পাটাতনে শুইয়ে দিয়ে ইচ্ছেমত প্রহার করে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে সে মায়ের পাশে শুয়ে থাকে।
“শরীরের ব্যথায় মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙ্গে, আবার ঘুম আসে এই অবচেতনার ফাঁকে কেবলই তার মনে হইতে থাকে সংসারে কেবল মা-ই সত্য আর কিছু না।”
প্রতিবাদী নারী বাসন্তী
বাসন্তী শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হবার পর বেশ কয়েকদিন ঘর থেকে বের হয় না। বাজারের লোকজন তথা কায়েতরা (যারা তামসীর বাপের বাড়িতে তবলা বাজায় তারা) তার সম্পর্কে নানারকম গুজব ছড়ায়। মঙ্গলার বউয়ের মুখ থেকে বাসন্তী সে-সব কথা শোনে। ‘কিন্তু সুবলার বউয়ের মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে।’ তাই সে সকল রকম মিথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মঙ্গলার বউ যখন বলে, ‘তুমি মাইয়া-মানুষ। তুমি কি করতে পার ভইন।’ তখন বাসন্তীর উত্তর- ‘আমি সব পারি। আর কিছু না পারি আগুন লাগাইয়া গাঁও জ্বালাইয়া দিতে পারি।’ বাসন্তী জানে অপমানের বাঁচার চেয়ে সম্মানের মৃত্যু অনেক ভাল। বাসন্তী লেখকের ভাষায় সত্যি ‘দমিতে জানে না’। মালোপাড়ার ছেলেরাও তার নীতিকে গ্রহণ করে কিন্তু কায়েতরা হয়ে ওঠে তাদের চরম শত্র”। গোপনে মালোদের নানারকম সর্বনাশের কাজে তারা অগ্রণী হয়।
ষড়যন্ত্র ও সর্বনাস
প্রবলের আধিপত্যে দুর্বলের অবসান- মালোপাড়ার মানুষদের জীবনেও এ সত্য প্রতিভাত হয়। রাতের অন্ধকারে মালোর ছেলেরা বাজারের বাবুদেরকে শাস্তি দিলে তারাও তাদের ওপর গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এই ষড়যন্ত্রের রেখা ধরে পারস্পরিক শত্রুতা চলে মালোদের সর্বস্বান্ত হওয়া পর্যন্ত। তেলিপাড়ার রজনীপাল তার মামা ঋণদান কোম্পানীর ফিশারি শাখার ম্যানেজারকে দিয়ে মালোদেরকে চক্রবৃদ্ধি সুদের টাকার জন্য নানারকম অত্যাচার চালাতে চায়।
‘দুরঙা প্রজাপতি’ পর্বেই মালোসমাজের সর্বনাশের শুর” আর ‘ভাসমান’ উপপর্বে সে-ভাঙন আরো স্পষ্ট হয়। ব্যক্তিস্বার্থ যখন মাথাচারা দিয়ে ওঠে তখন গোষ্ঠী-স্বার্থ ব্যাহত হয়। জীবন-জীবিকার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা না থাকলেও তাদের জীবনে একসময় বিচ্ছিন্নতা ছিল না। এখন তারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। সময়ের পরিবর্তনকে লেখক এখানে এড়িয়ে যাননি। ফলে সত্যকথন করতেও তিনি দ্বিধান্বিত নন।
মালোদের একতায় যেদিন ভাঙন ধরিল, সেইদিন হইতে তাদের দুঃসময়ের শুরু। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বজ্রের মত দৃঢ়; পাড়াতে তারা ছিল আঁটসাট সামাজিকতার সুদৃঢ় গাঁথুনির মধ্যে সংবদ্ধ। তাদের কেউ কিছু বলিতে সাহস করে নাই। পাড়ার ভিতর যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।
সামাজিক ভাঙনের সূত্রাবদ্ধ হয়েই যেন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু হয় মালোসমাজে। তামসীর বাপের বাড়িতে মালোদের শত্রুরা আরো শক্তভাবে জেঁকে বসে। গল্প গানে প্রবাদে ও লোকসাহিত্যের নানা কাহিনীতে ভরা মালোসমাজ ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উপাদান ছেড়ে চটুল অপসঙ্গীত ও নতুন যাত্রাপালার ভোক্তায় পরিণত হয়। ফলে মালোসমাজ সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের জায়গা থেকেও হয় দ্বিধাবিভক্ত। মালোপাড়ার একদল কালোবরণের বাড়িতে অন্যদল মোহনের বাড়িতে আসর জমায়।
মালোদের সাংস্কৃতিক শুদ্ধতার রক্ষা
মালোদের ঐতিহ্য ও গানের দৃঢ়তা তথা সাংস্কৃতিক শুদ্ধতা রক্ষা হয় অবশ্য মোহনের বাড়ির আসরকে ঘিরে। মালোপাড়ার মানুষ তবু কালোবরণের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অবক্ষয়ী সংস্কৃতির ভোক্তা হয়ে ওঠে। কালোবরণের বাড়ির হাসি তামাশা অভিনয়ে বেশির ভাগ মানুষ অংশগ্রহণ করে। মোহনের বাড়িতে ভাব ও কৃষ্ণভক্তির গান, দেহতত্ত্ব, হরিবংশ, নামগান, সহচরী গান, ভাইটাল কিংবা গোষ্ঠ গানে খুব একটা দর্শক সমাগম ঘটে না। এ-থেকেই বোঝা যায় মালোসমাজের সাংস্কৃতিক আবরণ কতটা খসে পড়েছে। কিন্তু মালোদের নিজস্ব ঋদ্ধ সংস্কৃতির একটা গভীরতা ও দীপ্তি ছিল। আজ তা নির্মিলিত প্রায়। লেখক মালোপাড়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটি ধারণা দিয়েছেন এ-পর্বে।
“…মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুর”ষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি যেমন মধুর, সুরও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে! আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সেই গানে সেই সুরে প্রাণ ভরিয়া তান ধরিলে চিত্তের নিভৃতিতে ভাব যেন আর আগের মত দানা বাঁধিতে চায় না, কোথায় যেন কিসের একটা বজ্রদৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়। যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।”
মোহনই কেবল মালোদের স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ‘কালের আঘাতের রুধিবার শক্তি কার আছে।’- একথা মোহনও জানে কিন্তু তাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রাণময় ভাবসম্পদের ওপর সে বিশ্বাস হারায় না। নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত সীমিত সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি তাই তাকে বিচলিত করে না। পরম সোৎসাহে সে গেয়ে চলে- ‘এহি বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণে বুঝিয়াছে দু’ নয়ানে। পশুপক্ষী সবে কান্দিছে নীরবে হায় হায় কৃষ্ণ বলে।’
তিতাসের পাড়ের মালো সংস্কৃতির পরাজয় ও মোহনের কান্না
কালের গতিকে ফেরানোর উপায় মোহনের নেই। দিন দুয়েক প্রতিযোগিতার পর মালোরা কালোবরণের বাড়ির সংস্কৃতিকে অভিনন্দন জানাল। পরাজয় হলো মালো-সংস্কৃতির; মোহনের কান্নায় আকাশ ভারী হলো। মোহনের চোখের জল লেখকের শুধু একার কষ্ট নয়; তিতাসপারের নিম্নজীবী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মালোসমাজেরও তা বেদনা।
দুই দিন পর যখন কালোবরণের বাড়িতে বাক্স বাক্স সাজ আসিল, এবং রাত্রিতে যখন সাজ পোশাক পরিয়া সত্যিকারের যাত্রা আরম্ভ হইল, মালোরা তখন সব ভুলিয়া যাত্রার আসর ভরিয়া তুলিল। বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ কেউ বাদ রহিল না। সকলেই গেল।
“এ-যাত্রাগানে যারা অংশগ্রহণ করল না তাদের একজন মোহন, অন্যজন সুবলার বউ বাসন্তী।”
তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি এবং আরও কিছু কথা
মালোদের সামাজিক ভাঙন ও সাংস্কৃতিক বিচ্যুতির পর দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক পরিবর্তন তাদের জীবনকে করে তোলে দিশেহারা। মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতি, মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ভাঙন কোনকিছুর চেয়েও কম নয় তিতাসের শুকিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। নদীর শুকিয়ে যাওয়ায় মানুষের কোন হাত নেই। তারপরও বলা যায় বিজ্ঞান শিখিয়েছে নদী শাসন। কিন্তু সামাজিক নিম্নকোটীর মানুষকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু আয়োজন প্রয়োজন তা দৃষ্টির অভাবেই ব্যাহত। তিতাসপারের একটি জনপদের ধ্বংসে কোনো ক্ষতি হয় না সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের। লেখক অদ্বৈত সে প্রশ্ন অবশ্য তোলেননি তাঁর উপন্যাসে। বরং একটি জনপদের মানুষের সীমাহীন দুঃখকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা চিহ্নায়িত করেছেন তা-ই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।
সাংস্কৃতিক অন্তর্বয়নের সূত্রে তিনি নির্দেশ করেন এখানকার নানা সাংস্কৃতিক উপাদানের। এসব সাংস্কৃতিক চিহ্নসমূহ মালোজীবনের ঘনিষ্ঠ বাস্তব হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শিল্পসম্ভব সত্যেরও প্রতিনিধিত্ব করে এর সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে তিতাস পাড়ের মালোদের মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিচয় মেলে; যেমন, ‘মাঘমণ্ডলের ব্রত’, ‘খলাবাওয়া’, ‘স্নানযাত্রা’, ‘জালাবিয়া’, ‘হোলি’, ‘উত্তরায়ণ সংক্রান্তি’, ‘কালীপূজা’, ‘পদ্মাপুরাণ পাঠ’, ‘মনসাপূজা’, ‘নৌকাবাইচ’ ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব মালোরা পালন করে। এসব সাংস্কৃতিক উৎসব তাদের জীবনধারণের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রেরণা থেকেও মালোসমাজ উৎসব পালন করে। স্থানু সমাজের মধ্যেও মালোসমাজের সংস্কৃতিসমূহ তাদের কার্নিভাল জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। প্রাকৃতজীবনের বোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় তা হয়ে ওঠে মালোদের অভিন্ন সংযোগ-সূত্র।
মালোরা জলের মালিক, মাটির মালিক নয়
মালোরা জলের মালিক তাই তিতাসের জল শুকিয়ে গেলে তারা মাটির আধিপত্য পায় না। ‘ভাসমান’ উপপর্বে লেখক নিরবলম্ব তরলের মালিক মালোদের সম্পর্কে এ-সত্যটি উদ্ঘাটন করেছেন :
“পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা, জেলেরা, গাছপালা বাড়িঘরের সঙ্গে মিতালী কর”ক, তারা বাষ্পের মত ভাসমান। যতই তারা পৃথিবীর বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকুক, ধরার মাটি তাহাদিগকে সর্বদা দুই হাতে ঠেলিয়া দিতেছে, আর বলিতেছে, ঠাঁই নাই, তোমাদের ঠাঁই নাই। যতদিন নদীতে থাকে জল, ততদিন জলের ওপর তারা ভাসে। জল শুখাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।”
ফলে তিতাসের বুকে চর জাগা নতুন মাটির মালিক হয় অনেক জমি যাদের আছে তারাই। তিতাসপাড়ের মানুষ একমুঠো অন্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির পথ পর্যন্ত বেছে নিতে বাধ্য হয়। সুব্লার বউয়ের কাছে সুতা কিনতে আর কেউ আসে না। তিতাসের বুকে স্নানের জল পর্যন্ত হয় অপ্রতুল, মাছের পরিবর্তে জালে উঠে আসে দু চারটি মৌরলা কিংবা একপাল ব্যাঙ। মালোপাড়ায় দুর্ভিক্ষ নামে। আধিপত্যবাদিতার ধাক্কার চরমসীমানায় পৌঁছে মালোরা সমাজ-সাংস্কৃতিক সংযোগসূত্র হারায়। পরস্পরের একতাবোধও নস্যাৎ হয়ে যায়। একদিকে এটি অনিবার্য যে তিতাস শুকিয়ে না গেলেও মালোপাড়ার সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসত। অন্যদিকে প্রবল সমাজ-অর্থনীতির সত্য মালোদের বিপর্যস্ত জীবনে কার্যকর। লোন কোম্পানির লোকরা মালোদের দুর্বলতার সুয়োগ নিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে। জীর্ণদেহী রামকেশব বৃদ্ধকেও তারা রেহাই দেয় না। রাধাচরণ মালো দুঃস্বপ্ন দেখে। মালোদের নানা দুঃস্বপ্ন সত্য বলে ফলে যায়। নিরবলম্ব জীবনের এইসব অসহায়ত্বের বর্ণনা তিতাসপাড়ে ঘনিয়ে ওঠা এক বাস্তব ইতিহাস যা কাতর মানুষের কান্নায় অভিষিক্ত।
সর্বশান্ত তিতাস নদীর পাড়ের মানুষ
প্রবল বন্যায় তিতাসপাড়ের মানুষ সর্বস্বান্ত। অনেকে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যায়। অনন্তবালাও গ্রাম ছেড়ে আসামের পথে রওনা হয়। অনন্তের খবর পাওয়া যায়- সে বাবুদের সঙ্গে মিশে লোকের উপকার করে ফিরছে। মালোপাড়ায় যারা থাকে তাদেরও কেউ বেঁচে থাকে না শুধু বাসন্তী আর রামকেশব এ দু জন ছাড়া। বাসন্তী দুঃস্বপ্নের মত ঘটমান বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসে বাসন্তীর কিন্তু ততক্ষণে ‘জলভরা লোটা তার শিথিল হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে।’ বাসন্তীর হাত থেকে জলভরা লোটা পড়ে যাবার বিষয়টি প্রতীকী। আসলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া মানুষের প্রতিরূপ বাসন্তী। জীবনের সমস্ত বাধন আলগা হয়ে আজ তার বেঁচে থাকা নিরর্থক। উপন্যাসের শেষের বাসন্তীর কর”ণ দৃশ্য অঙ্কনের মধ্য দিয়ে সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত মালোপাড়া শুধু চোখে ভাসে।
‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের নায়ক এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ
অনন্তের মধ্য দিয়ে লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের নিজস্ব বেদনা ও অনুভব সঞ্চারিত হয়েছে বলে দৃষ্টিগোচর হয়। এ-উপন্যাসের নায়ক অনন্ত কি না এ-নিয়েও সংশয় জাগে।
আসলে প্রথাগত উপন্যাসের কাঠামোবদ্ধ করে লেখক উপন্যাস রচনা করেননি। বাংলাদেশে কিংবা অন্যদেশেও হাজারো মালোপাড়া রয়েছে। নিম্নজীবী এসব মানুষের ভালবাসা যন্ত্রণা হাসি কান্না সবই কোথায় মিলিয়ে যায় তার হদিস কেউ রাখে না। লেখক এই জনগোষ্ঠীতে না জন্মালে এদের জীবনযাপনের ইতিহাসও থাকত ডালে শুকিয়ে যাওয়া পাতার মত। ফলে তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে যা কিছু ঘন হয়ে উঠেছে তা এখানকার মানুষের নিয়ত দুঃখ-যন্ত্রণা, জীবিকার তাগিদ আর ধ্বসে যাওয়া এক বাস্তবতার ইতিকথা। উপন্যাসের গঠনের দিক থেকে তিনি সচেতনভাবে কোনকিছু ভেবে অথবা সমকালীন যুগের ঔপন্যাসিকদের মত চরিত্রকে মায়াবী প্রেমের রঙতুলির আঁচড় দেয়া হয়ত সমীচীন মনে করেননি। তাঁর নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতাই এ-উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে সত্য করে তুলেছে। একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-মরণই সেখানে মুখ্য। লেখক নিজে শুধু অমর হয়ে থাকেননি, থেকেছে তাঁর তিতাসপাড়ের মানুষ। এটাই অদ্বৈত মল্লবর্মণের এ ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের বিশেষত্ব। তাঁর শিল্পের সত্য তিনি নিজে। তাই উপন্যাসের নায়ক কে তা নির্ধারণ করা একটি জটিল কর্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। সুবল কিশোর বা অনন্ত কারো মধ্যেই আসলে প্রথাগত বাংলা উপন্যাসের নায়ক হবার গুণ নেই। আবার এটাও সত্য তারা যে কাহিনীর মহানায়ক তাতে রোমান্টিক খাপছাড়া আর দশটা নায়কের চেয়েও জীবনধর্মের বেশি কাছাকাছি। কিশোরের পাগল হওয়া, তার উন্মত্ত হওয়া, হোলির দিনে পাগলামী করা এ সবই বাস্তব মানুষের ছায়া। বাস্তবেই কোন রঙ চড়াবার কাহিনী তাতে নেই। সুবলের মৃত্যু অকালে ঝরে পড়া এক দরিদ্র পিতা-মাতার বেদনার অসীম ভারবাহী; সে-সঙ্গে সমাজ-অর্থনীতির দণ্ডমুণ্ডকর্তাদের নির্লজ্জ বাণিজ্য বেসাতির কুপরিণাম। কালোবরণরা শুধু সুবলের হত্যাকারী নয় তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নিয়ামক। সুবল কিশোর অকালে ঝরে পড়লেও অনন্তকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অনন্তের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনের ছায়া থাকা অসম্ভব নয়। পিতৃমাতৃহীন অনন্ত লেখকের ব্যক্তিগত দুঃখবোধের মর্মসঙ্গী। অনন্তর প্রেম তার বাবা কিশোরের মতই অপরিণত। এ-উপন্যাস আসলে হয়ে উঠেছে জেলে-জীবনের গাঁথা। ফলে অনন্তবালার মধ্যে যে প্রেমের অঙ্কুর তা শুধু অপেক্ষায় নিরুদ্ধ।
অনাস্বাদিতপূর্ব প্রেমের অজানা এক রহস্যলোকের অনুভূতি অনন্তের হৃদয়ে জাগ্রত হলেও পড়াশুনার জন্য শহরে যাবার বাস্তবতা তাতে ছেদ ঘটায়। উপন্যাসের ‘ভাসমান’ উপপর্বে অদ্বৈত সে কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শিক্ষার্জন কিংবা বিদ্বান হবার বাসনা তার ভেতরে জাগায় নিম্নশ্রেণীরই মানুষ নাপিতানী। এ তো নিম্নবিত্তের পক্ষে স্বপ্ন-সম্ভাব্যতার পথে যাত্রা সূচনা। ফলে অনন্তকে সে কাছে নয় দূরের শহর কুমিল্লায় যেতে বলে। অনন্তবালা তাকে জোর করে নিজের বাড়িতে ধরে রাখতে চেয়েছিল। অনন্তবালার মা তার নাম বদলে রাখতে চেয়েছিল হরনাথ, ছোটোখুড়ি পিতাম্বর। কিন্তু অনন্ত আর কারো শাসনে ধরা দেবে না। মাসী বাসন্তীর কাছ থেকে যার স্নেহের বাঁধন টুটে গেছে সে অনন্তের আর স্নেহের শাসন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আলোকময় এক পৃথিবীর দিকে অব্যহতযাত্রায় মনস্থ অনন্ত। কিন্তু আলোকিত পৃথিবীর উপাদান নিয়ে ফেরা অনন্তের ভেতর শেষপর্যন্ত থাকল হতাশা। মালোসমাজে মেয়েকে আইবুড়ি করে রাখার নিয়ম নেই। বনমালীকে যেতে হলো অনন্তের খোঁজে কুমিল্লা স্টেশনে। কিন্তু সাতবছর পর অনন্তের সঙ্গে তার দেখা হয়। অনন্তকে তারা তাদের দুঃখের কাহিনী শোনায়। এ- যেন এক বিষণ্ণ বাস্তব। তাদের আরজির ভাষা লেখক তুলে ধরেন :
“…আমাদের অনন্ত না জানি কোথায় আছে। সে কি জানে না তিতাস নদী শুখাইয়া গিয়াছে, মালোরা দলছাড়া মীনের মত হইয়াছে। খাইতে পায় না মাথার ঠিক নাই। অনন্ত লেখাপড়া শিখিয়াছে, সে কেন আসিয়া গরমেন্টের কাছে চিঠি লিখিয়া, মালোদের একটা উপায় করিয়া দেয় না। হায় অনন্ত, তুমি যদি একবার আসিয়া দেখিতে তিতাসতীরের মালোদের কি দশা হইয়াছে।”
শেষ কথা
অদ্বৈত মল্লবর্মণের ব্যক্তিজীবন থেকে জানা যায় তিনি সারাজীবন তাঁর মুষ্টিঅন্ন অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন। মালোপাড়ার কেউ তাঁর কলকাতার বাড়িতে পৌঁছালে তিনি তাদেরকে যথাসাধ্য সম্মান ও অর্থ সাহায্য করেছেন। তবুও অনন্তের মধ্যে যে বেদনাবোধের সঞ্চার তিনি করেছেন তা তার নিজস্ব জনগোষ্ঠীর প্রতি ঐকান্তিক অনুভব-যাতনা। ধ্বংসপ্রাপ্ত মালোসমাজের অস্তিত্বের সঙ্গে লেখকের নিজস্ব আত্মা যেন জড়িয়ে পড়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে- প্রচণ্ড অসুস্থতা নিয়েও হাসপাতাল থেকে পালিয়েছিলেন কেন তিনি? এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। শেষাবধি তিনি কি শেকড়-সন্ধান করতে গিয়ে বাস্তুচ্যুতির দায়ে পরাজিত সত্তা? অদ্বৈত মল্লবর্মণের শেকড়চ্যুতি ঘটেছিল মালোসমাজের ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ লেখক অদ্বৈত স্বল্পায়ু হয়ে তাই নিরব অভিমানে বিদায় নিলেন।